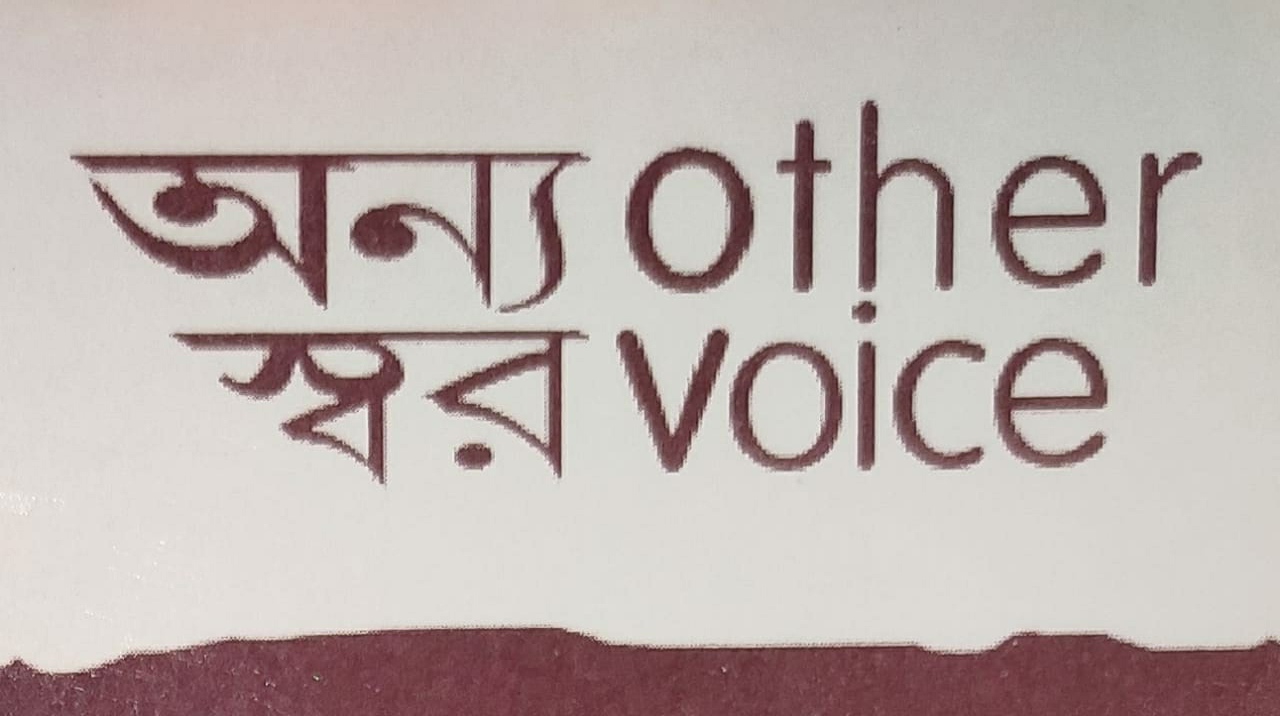রবীন্দ্র ছোটগল্প : ভারতী পত্রিকা পর্ব
- 07 August, 2025
- লেখক: সৌভিক ঘোষাল
১২৯৮ থেকে ১৩০২ পর্যন্ত প্রথমে হিতবাদী ও তারপর মূলত সাধনা পত্রিকায় পাঁচবছর ধরে একটানা অনেকগুলো গল্প লেখার পর দু বছরের বিরতি আসে রবীন্দ্র গল্প রচনায়। ১৩০৫ বঙ্গাব্দের বৈশাখে আবার ‘ভারতী’ পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ গল্প লেখা শুরু করলেন। লিখলেন পরপর বেশ কিছু গল্প। ১৩০৫ এ ভারতী পত্রিকায় বেরোল ‘দুরাশা’, ‘পুত্রযজ্ঞ’, ‘ডিটেকটিভ’, ‘অধ্যাপক’, ‘রাজটীকা’, ‘মণিহারা’, ‘দৃষ্টিদান’ - এই সাতটি গল্প। ১৩০৭ এ আবার ‘ভারতী’তে লিখলেন ‘উদ্ধার’, ‘দুর্বুদ্ধি’, ‘ফেল’ এই তিনটি গল্প আর প্রদীপ পত্রিকায় লিখলেন ‘সদর ও অন্দর’ এবং ‘শুভদৃষ্টি’ নামে দুটি গল্প। ভারতীতে ১৩০৮ বঙ্গাব্দের বৈশাখ থেকে অগ্রহায়ণ পর্যন্ত আট সংখ্যা জুড়ে বেরোল রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প ‘নষ্টনীড়’। ১৩০৯ সালে প্রকাশিত বঙ্গদর্শন পত্রিকায় বেরোল দুটি গল্প – ‘দর্পহরণ’ ও ‘মাল্যদান’। ভারতী, প্রদীপ ও বঙ্গদর্শন মিলিয়ে ১৩০৫ থেকে ১৩০৯ এই পাঁচ বছর সময়কালে প্রকাশিত পনেরোটি গল্পকে আমরা বলতে পারি ভারতী পর্বের গল্প। অনেক পরে ১৩১৮ বঙ্গাব্দে রাসমণির ছেলে ও পণরক্ষা নামে দুটি গল্প লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু সেগুলো সাধনা ভারতী পর্ব ও সবুজপত্র পর্বের মধ্যবর্তী পর্যায়ের গল্প হিসেবে আলাদাভাবে বিবেচ্য।
‘দুরাশা’ গল্পটির মধ্যে বঙ্কিমী গল্পের আমেজ আছে, রয়েছে ইতিহাসকে ব্যবহার করে আখ্যানকে জমিয়ে তোলার কৌশল৷ অবশ্য ১৮৫৭ র সিপাহী বিদ্রোহ বা মহাবিদ্রোহের উতরোল সময়ের প্রেক্ষাপটকে আশ্রয় করে এই গল্প লেখা হলেও এটি মূলত এক বিয়োগান্তক প্রেমের গল্প। বঙ্কিমের পরবর্তী পর্যায়ের লেখায় হিন্দুত্ববাদী সুর এলেও প্রথম পর্বে ‘দুর্গেশনন্দিনী’ বা ‘কপালকুণ্ডলা’য় হিন্দু মুসলিমের মধ্যে প্রেম সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল মানবধর্মের স্বাভাবিক প্রবণতায়। প্রেম সেখানে ধর্মের ভেদ দেখে নি। রবীন্দ্রনাথের দুরাশা গল্পেও ধর্মের বেড়া টপকেই মুসলমান নবাবপুত্রী প্রেমে পড়েছিল নবাব ফৌজের সেনাপতি হিন্দু ব্রাহ্মণ কেশরলালের। যখন ইংরেজদের বিরুদ্ধে সিপাহী বিদ্রোহ শুরু হল কেশরলাল প্রাণপণে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়লেন কিন্তু নবাব করে বসলেন বিশ্বাসঘাতকতা। ইংরেজদের কাছে গোপনে তার সেনা ও সেনাপ্রধানের বিদ্রোহের খবর পাঠিয়ে দিলেন। ইংরেজরা খবর পেয়ে পালটা আক্রমণ শানাল অতর্কিতে। পরাস্ত, মারাত্মক আহত হয়ে মৃতপ্রায় কেশবলালকে দেখে শিউরে ওঠে নবাবনন্দিনী। তার মুখে জল দেয়। শুশ্রূষায় প্রাণ ফিরে পায় কেশবলাল। কিন্তু বিশ্বাসঘাতকের নবাবের কন্যাকে সে সহ্য করতে পারে না। তীব্র বিবমিষা থেকে তাকে আক্রমণ করতে টেনে আনে ভিন্ন ধর্ম পরিচয়। কটূ কথা বলে, আঘাত করে অজানার উদ্দেশ্যে হারিয়ে যায়। এরপর নবাব নন্দিনী বহুবছর সন্ধান করেন কেশবলালের। কেশবলালের ধর্মের সঙ্গে নিজেকে মেলানোর জন্য হিন্দু শাস্ত্র পড়েন, হিন্দু যোগিনীর বেশও ধারণ করেন। কিন্তু যে জন্য এত বদল সেই কেশবলালকে তিনি কোথাও খুঁজে পান নি। বহু বছর পর যখন তাঁকে দেখতে পেলেন তখন সেনাপ্রধান বীর কেশবলাল রূপান্তরিত হয়েছেন এক সাধারণ গ্রাম্য কৃষকে। এক সাধারণ কুটীরে ভুটিয়া স্ত্রী ও পরিবার নিয়ে সংসার নির্বাহ করছেন নিতান্ত আটপৌরে ভাবে। অন্যদিকে মুসলিম নবাব নন্দিনী জীবনের প্রেম হারিয়ে পরিণত হয়েছেন পথে পথে ঘুরে বেড়ানো গেরুয়া বসনধারী সন্ন্যাসিনীতে।
‘পুত্রযজ্ঞ’ গল্পের প্রথম অংশে অল্প পরে লেখা বিখ্যাত নষ্টনীড় গল্পের একটুখানি আভাস দেখা যায়, তবে এর বুনোট বা পরিণতি অংশটি একেবারেই অন্য স্তর ও মাত্রার। মিলের জায়গাটা সামান্যই - নষ্টনীড়ে চারুর নি:সঙ্গতা এবং সেইসূত্রে দেবর অমলের সঙ্গে তার নিবিড় নৈকট্যর মতোই এখানে এসেছে যুবতী বিনোদিনীর একাকিত্বের কথা। তবে ইন্টেলেকচুয়াল ভূপতি আর মোটাদাগের মানুষ বৈদ্যনাথের ফারাক এমনই আসমান জমিন, নষ্টনীড়ের অনুপুঙ্খ বিস্তার ও গভীরতার পাশে পুত্রযজ্ঞের অল্প কটি অনুচ্ছেদ এমনই সাধারণ, যে এই দুইয়ের বস্তুত কোনও তুলনাই হয় না। ‘পুত্রযজ্ঞ’ গল্পের বিনোদিনীর স্বামী বৈদ্যনাথ প্রেম বুঝত না, বিবাহকে কেবল সন্তানলাভের জৈবিক উপায় হিসেবেই দেখত। বিয়ের বেশ কিছুদিন পরেও বিনোদিনী সন্তান সম্ভবা না হওয়ায় সে বিরক্ত এবং ক্ষুব্ধ হল৷ শ্বশুরবাড়ির অন্যদের মানসিকতাও ছিল সেরকমই। ফলে স্নেহ এবং স্নিগ্ধতার বদলে তর্জন গর্জন ই বিনোদিনীর সব সময়ের সঙ্গী হল। এই মরুভূমিতে একমাত্র মরুদ্যান ছিল প্রতিবেশী কুসুমের বাড়িতে তাস খেলতে যাওয়া ও বন্ধুসঙ্গ। শুধু বন্ধুই নয় এখানে সে পেয়ে গেল তার প্রতি আকৃষ্ট এক পুরুষকেও। তাস খেলতে খেলতেই কুসুমের তরুণ দেবর নগেন্দ্র আর বিনোদিনী ক্রমশ পরস্পরের কাছে এল। যৌবন আকাঙ্ক্ষায় উন্মত্ত হয়ে একদিন নগেন্দ্র বিনোদিনীকে সবলে বুকে টেনে চুম্বন পর্যন্ত করল, কিন্তু তা চোখে পড়ে গেল অন্য লোকের। বিনোদিনীকে কলঙ্কিনী অপবাদ দিয়ে শ্বশুরবাড়ি থেকে দূর করে দেওয়া হল। এর পেছনে পরপুরুষের জোর করে দেওয়া একটা চুম্বনের চেয়েও বেশি অপরাধ বলে গণ্য হল ইপ্সিত সন্তান স্পম্ভাবনা তৈরি না হওয়া। রবীন্দ্রনাথ দেখালেন নিয়তির অদৃশ্য হাসি কীভাবে এখানে লুকনো ছিল। বিনোদিনী নিজে বা অন্য কেউও তখন জানতে পারে নি সে স্বামীর বীজ ধারণ করে গর্ভবতী হয়েছে। যথাসময়ে সেই সন্তানের জন্ম হল এবং অনাথ অবস্থায় পথের ভিখারির মতো বড় হতে থাকল। অন্যদিকে বিনোদিনীর স্বামী বৈদ্যনাথ আরো তিনটি বিয়ে করলেন কিন্তু সন্তান সুখ পেলেন না। সন্তান কামনায় বাড়িতে যাগযজ্ঞ শুরু হল ঘটা করে। এরকম এক যজ্ঞের সময় বিনোদিনী মলিন বেশে পথের ভিখিরির মতো তার ছেলেটিকে নিয়ে সেখানে হাজির হল একটু খাবারের আশায়। তাদের চিনতে না পেরে সবাই তাদের তাড়িয়ে দিল। রবীন্দ্রনাথ গল্পের শেষ বাক্যে ভাগ্যের নিখুঁত আয়রনিকে প্রকাশ করলেন - "একশত পরিপুষ্ট ব্রাহ্মণ এবং তিনজন বলিষ্ঠ সন্ন্যাসী বৈদ্যনাথকে পুত্রপ্রাপ্তির দুরাশায় প্রলুব্ধ করিয়া তাহার অন্ন খাইতে লাগিল"।
রবীন্দ্রনাথের অসামান্য ছোটগল্পগুলির পাশেই আছে কিছু অকিঞ্চিৎকর রচনা। ডিটেকটিভ তেমনই একটি। বাল্যকালের মুগ্ধতা বিবাহে পরিণতি পায় নি, কিন্তু না পাওয়ার আক্ষেপ মনে থেকে গিয়েছে - এই থিমটি রবীন্দ্রনাথের গল্পে বেশ কয়েকবার ঘুরে ফিরে এসেছে। এই প্রসঙ্গে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নি:সন্দেহে ‘একরাত্রি’। ‘ডিটেকটিভ’ গল্পের শেষে এসে আমরা জানতে পারি এখানেও এমন ইচ্ছা অপূরণ জনিত দীর্ঘশ্বাস আছে, কিন্তু সেটি গল্পের মূল কাঠামোতে দেখানো হয় নি, শেষে বিবৃতির মতো করে খানিক তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে। এই গল্পে পুলিশের এক গোয়েন্দার স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের গোয়েন্দাদের মতো বিখ্যাত হয়ে ওঠার স্বপ্ন ও চেষ্টাকেই বরং খানিকটা উপহাস করা হয়েছে। গল্পকথক মহিমচন্দ্র ভেবেছিল সে সন্দেহজনক গতিবিধির সূত্র ধরে একটি সম্ভাব্য অপরাধের কিনারা করতে যাচ্ছে। কিন্তু সে বুঝতেই পারে নি এই গতিবিধির সঙ্গে তার স্ত্রীর এক পরিচিতই যুক্ত এবং এর মধ্যে পরকীয়া বা বে আইনী কোনও ব্যাপার নেই৷ গল্পের শেষে যখন একটি চিঠি পড়ে সে প্রকৃত সত্য জানতে পারল, তখন বিখ্যাত সত্যান্বেষী বা গোয়েন্দা হবার স্বপ্ন থেকে সে নিজেকে বেকুবের স্তরে স্খলিত হতে দেখল।
ভারতী পর্বের বেশ কয়েকটি ছোটগল্পেই রয়েছে গল্পকথকের গল্প শেষে বেকুব বনে যাবার হাস্যকর পরিণতি৷ অধ্যাপক গল্পটিও এমনই এক গল্প। কলেজ পড়ুয়া মহীন্দ্রকুমার এই গল্পের কথক। সে প্রথম যৌবনের স্পর্ধায় নিজেকে খুব বড় লেখক ও প্রাজ্ঞ ভাবতে শুরু করেছিল। যে সব নিবন্ধ রচনা করে সে সভাসমিতিতে পড়ত, অজ্ঞ স্তাবকরা তার খুব প্রশংসা করত। কিন্তু বামাচরণবাবু নামের এক প্রাজ্ঞ অধ্যাপক যখন সভায় হাজির হয়ে দেখিয়ে দিলেন মহীন্দ্রকুমারের প্রবন্ধের অনেকটাই অন্য লেখকের থেকে সরাসরি টোকা আর বাকী নিজের লেখা অংশটি নেহাৎই সাদামাঠা – তখন স্তাবক মহলে তার মাথা কাটা গেল। মননশীল প্রবন্ধে নয়, সৃজনশীল কাব্য আখ্যান জগতেই সে আলোড়ন তুলবে – এমন অভিপ্রায় নিয়ে মহীন্দ্রকুমার বি এ পরীক্ষা শেষে চলে গেল ফরাসডাঙা বা চন্দননগরের গঙ্গাতীরের এক নির্জন বাড়িতে। প্রতিবেশী হিসেবে সে পেল ভবনাথবাবু নামের এক প্রৌঢ় প্রাজ্ঞকে আর মন দিয়ে বসল তার যুবতী কন্যা কিরণবালাকে। কিরণকে জ্ঞানের ছটা জাহির করে আকৃষ্ট করার চেষ্টা চালিয়ে গেল মহীন্দ্রকুমার, তবে দেখা গেল দর্শন সাহিত্য নিয়ে জ্ঞানগম্ভীর আলোচনা এড়িয়ে প্রাত্যহিক কাজের আলাপেই কিরণের উৎসাহ বেশি। গল্পের একেবারে শেষে এসে আমরা জানতে পারি কিরণ একজন দেদীপ্যমান ছাত্রী, বি এ পরীক্ষায় যেখানে মহীন্দ্র অনুত্তীর্ণ হল সেখানে কিরণ শুধু পাশই করল না, সেকালে অতিবিরল একেবারে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হবার কৃতিত্ব অর্জন করল। এও জানা গেল উচ্চশিক্ষার মতো নিজের প্রেমজীবনকেও সে মহীন্দ্রর কাছে সম্পূর্ণ গোপন রেখেছিল। একেবারে শেষে এসে সে জানতে পারল কিরণ সেকালের নামজাদা অধ্যাপক এবং তার কুম্ভীলকবৃত্তি ধরে ফেলা প্রাজ্ঞ বামাচরণের বাগদত্তা। যশ ও প্রেম দুই আকাঙ্ক্ষাই এভাবে ধ্বস্ত হবার পর মহীন্দ্রর অনুভূতিকে ব্যঞ্জনায় গল্পশেষে প্রকাশ করলেন রবীন্দ্রনাথ – “রাত্রে বাড়িতে আসিয়া আমার রচনাবলীর খাতাখানা পুড়াইয়া ফেলিয়া দেশে গিয়া বিবাহ করিলাম।
গঙ্গার ধারে যে বৃহৎ কাব্য লিখিবার কথা ছিল তাহা লেখা হইল না, কিন্তু জীবনের মধ্যে তাহা লাভ করিলাম”।
ব্রিটিশ আমলে বাবু ভদ্রলোক কীভাবে একদিকে ইংরাজের প্রতি ভয়ভক্তি ও নবজাগ্রত ভীরু সাবধানী স্বদেশপ্রেমের মধ্যে দোদুল্যমান থাকত, তার এক মজার ছবি রয়েছে ‘রাজটীকা’ গল্পে। গল্পের নায়ক নবেন্দু কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের সম্মেলন উপলক্ষ্যে অনেকটা চাঁদা দিয়েছিল কংগ্রেস করা শ্যালকের অনুরোধ উপরোধ এড়াতে না পেরে। এই চাঁদা দেবার খবর খবরের কাগজে বের হলে যেমন সে শ্লাঘা বোধ করল, তেমনি ব্রিটিশভক্ত কাগজে এই নিয়ে বিরূপ আলোচনা বেরোলে সে বিড়ম্বিত হল। তার বড়শালিকা পরিবারের অন্যদের মতোই ছিলেন নবজাগ্রত স্বদেশপ্রেমে মগ্ন। সেইসঙ্গে তিনি ছিলেন অসম্ভব বুদ্ধিমতি ও পরিহাসপ্রবণ। কয়েকজনকে হাবিলদারের পোশাক পরিয়ে কংগ্রেসকে চাঁদা দেবার জন্য ম্যাজিস্ট্রেট তলবের যে মজাদার নাটক তিনি তৈরি করেছিলেন, তা নবেন্দুকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল। প্রাক মহাত্মা গান্ধী, এমনকী প্রাক বঙ্গভঙ্গ যুগে কিছু নিরাপদ স্বাদেশিক আলোচনা ও মূলত ডেপুটেশন দেবার দল হিসেবে সীমাবদ্ধ থাকা উনিশ শতকী কংগ্রেস ও তার বাবু সদস্যদের চরিত্রের নির্মোকটি এখানে রবীন্দ্রনাথ অনেকটাই খসিয়ে দিয়েছেন।
মণিহারা হল নারীর পুঁজিরতির গল্প এবং এই অর্থে ব্যতিক্রমী। নারীকে প্রেম ভালোবাসার কাঙাল হিসেবেই যখন সাহিত্যে আঁকা হত, তখন এই গল্পে রবীন্দ্রনাথ দেখালেন ফণিভূষণের স্ত্রী মণিমালিকা স্বামীর ঘর ছাড়ছে এক অন্যরকম কারণে। এর পেছনে না আছে স্বামী বা শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের নির্যাতন, না আছে কোনও গোপন প্রেমের অমোঘ টান। স্বামী ব্যবসা সঙ্কটের কারণে মণিমালিকার কাছে তাঁর অলঙ্কারগুলি চান এবং স্বামীগৃহে থাকলে সেগুলি তাঁকে দিয়ে দিতে হবে এটা বুঝে সে গয়নাগাঁটি নিয়ে স্বামীগৃহ ত্যাগ করে। নারীর অলঙ্কারপ্রিয়তার সাধারণ ছবি থেকে এই অলঙ্কাররতি আলাদা গোত্রের ও ব্যতিক্রমী।
দৃষ্টিদান রবীন্দ্রনাথের এক আশ্চর্য সুন্দর গল্প যা নায়িকা কুমুদিনীর ব্যথায় পাঠককে ব্যথিত করে, আবার সর্বংসহা রূপ ছেড়ে যখন সে আত্মপ্রত্যয় নিয়ে উঠে দাঁড়ায়, তখন তাকে সাবাসিও জানায়। কুমুদিনীর স্ত্রী জীবনের প্রথম পর্বটি ছিল স্বামীভক্তির প্রচলিত ছকে আবদ্ধ। চোখের ভুল চিকিৎসা করে ডাক্তারী পাঠরতা স্বামী তার চোখ দুটি নষ্ট করে দেন। কুমুর দাদার পরামর্শ, অন্য ডাক্তার দেখানোর অনুরোধ কোনও কিছুকেই তিনি তখন অবধি প্রশ্রয় দেন নি। স্বামী যাতে রাগান্বিত না হন তাই কুমু দাদার দেওয়া ওষুধও খায় নি। চোখ নষ্ট হয়ে যাওয়ার পরও সে স্বামীকে কোনওরকম দোষারোপ করে নি।
কুমু স্বামীর বিরুদ্ধে চলে গেল যখন তার স্বামী ভেতর থেকে বদলে গেলেন এবং আচরণে ও চিন্তায় সংকীর্ণ মানসিকতা ও লোভ প্রকাশ করতে শুরু করলেন। চিকিৎসক হয়ে তাঁর পসার যত জমল, তত তিনি লোভি হলেন এবং চড়া অর্থমূল্য ব্যতীত রোগী দেখতে অস্বীকার করতে শুরু করলেন। যে স্বামী একসময়ে বলেছিল শুধু জীবিকার জন্যই নয়, গরীব মানুষের সেবার জন্যই তার চিকিৎসক হওয়া, তার এই অধঃপতন কুমু মানতে পারে নি। একসময়ে সে এসব দেখে নিজের মধ্যে গুমরে মরেছে, গোপনে অর্থসাহায্য করেছে স্বামীর কাছ থেকে চিকিৎসা না পেয়ে ফিরে যাওয়া রোগীর পরিজনকে। কিন্তু তারপর সে স্বামীর কার্যকলাপের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে শুরু করেছে। স্বামী যখন দ্বিতীয় বিবাহ উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছেন, তখন সে সর্বাত্মক দৃঢ়তায় বাধা দিয়েছে। এইখানে জেগে উঠেছে তার প্রতিবাদী সত্তার নতুন রূপ। রবীন্দ্রনাথের গল্পে সাধারণভাবে ইচ্ছাপূরণধর্মী সমাপ্তি থাকে না। এই গল্পটি সেদিক থেকে ব্যতিক্রম। হৈমি শেষপর্যন্ত কুমুর সতীন না হয়ে উঠে ঘটনার নাটকীয় বদলে হয়ে উঠল ভাতৃবধূ, যে ভাই ছিল ইজজীবনে তার সবচেয়ে সহায় ও শুভাকাঙ্ক্ষী। হৈমির মধ্যে স্নেহময়ী বোনকেই শুধু কুমু খুঁজে পেল না, স্বামী চরিত্রেও এলো নতুন উপলব্ধি ও বদল। কুমুর আত্মপ্রত্যয়ে জেগে ওঠা যেন এইভাবে গল্পশেষে পুরস্কৃত হল আর পাঠককে দিল স্বস্তি।
ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত উপরোক্ত গল্পগুলির পাশাপাশি এইসময়ে রবীন্দ্রনাথ প্রদীপ পত্রিকায় লেখেন দুটি ছোট গল্প। একটি হল ‘সদর ও অন্দর’। রাজা রাণী ও রাজপরিবারে আশ্রিত একজনকে নিয়ে এই গল্প আদপেই কোনও রাজকাহিনী নয়, মানবমনে প্রীতি ও ঈর্ষার যে আশ্চর্য খেলা চলে তারই উদ্ভাসন। রাজা বিপিন বলে একজনকে আশ্রয় দিয়েছিলেন ও তার সঙ্গে গান গল্পে অনেক সময় কাটাতেন, রানীর কাছে বিপিনের অনেক সুখ্যাতি করতেন। রানীর ভালোবাসায় বিপিন ভাগ বসাচ্ছে এটা রানীকে খুশি করে নি। বিপিনের প্রশংসা তার ভালো লাগত না। রাজা রানীর এই ঈর্ষাকাতর মূর্তিটি দেখে আমোদ পেতেন। এক নাটকের অনুষ্ঠানে বিপিনের অভিনয় দেখে রানী স্বয়ং যখন মুগ্ধ হলেন ও বিপিনকে কদর করতে শুরু করলেন, তখন রাজার মনোভাব গেল একেবারে বদলে। এইবার রানীর প্রশংসা তাঁকে বিঁধল এবং রানীর প্রশংসাপ্রাপক বিপিনকে আর সহ্য করতে না পেরে তিনি দূর করে দিলেন।
প্রদীপ পত্রিকায় প্রকাশিত দ্বিতীয় গল্পটি হল উদ্ধার। এই গল্পটি গৌরীর সূত্র ধরে নারী মনের বিচিত্র মনস্তত্ত্বের আভাস দেয় পাঠককে। পরেশ আর গৌরীর দাম্পত্যে সমস্যার কাঁটা হয়ে প্রবেশ করলেন গুরুদেব পরমানন্দ। আগে থেকেই পরেশ সন্দেহবাতিকগ্রস্থ ছিলেন ও চাকরবাকরদের সন্দেহের বশে তাড়িয়ে দিতেন। কিন্তু পরমানন্দকে নিয়ে সন্দেহ পৌঁছল ঈর্ষার স্তরে এবং সেই ঈর্ষা আক্রমণাত্মক ভাষায় আত্মপ্রকাশও করল। “একদিন সামান্য কারণে বিষ উদ্গীরিত হইয়া পড়িল। স্ত্রীর কাছে পরমানন্দকে উল্লেখ করিয়া 'দুশ্চরিত্র ভণ্ড' বলিয়া গালি দিলেন এবং কহিলেন, 'তোমার শালগ্রাম স্পর্শ করিয়া শপথপূর্বক বলো দেখি সেই বকধার্মিককে তুমি মনে মনে ভালোবাস না।” চাপান উতোর বাড়ল। “দলিত ফণিনীর ন্যায় মুহূর্তের মধ্যেই উদগ্র হইয়া মিথ্যা স্পর্ধা দ্বারা স্বামীকে বিদ্ধ করিয়া গৌরী রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, 'ভালোবাসি, তুমি কী করিতে চাও করো।' পরেশ তৎক্ষণাৎ ঘরে তালাচাবি লাগাইয়া তাহাকে রুদ্ধ করিয়া আদালতে চলিয়া গেল”। এরপর ঘটনা এগোল বিদ্যুৎগতিতে।
“পরমানন্দ নিভৃত ঘরে জনহীন মধ্যাহ্নে শাস্ত্রপাঠ করিতেছিলেন। হঠাৎ অমেঘবাহিনী বিদ্যুল্লতার মতো গৌরী ব্রহ্মচারীর শাস্ত্রাধ্যয়নের মাঝখানে আসিয়া ভাঙিয়া পড়িল।
গুরু কহিলেন, 'এ কী।'শিষ্য কহিল, 'গুরুদেব, অপমানিত সংসার হইতে আমাকে উদ্ধার করিয়া লইয়া চলো, তোমার সেবাব্রতে আমি জীবন উৎসর্গ করিব।'
পরমানন্দ কঠোর ভর্ৎসনা করিয়া গৌরীকে গৃহে ফিরিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু, হায় গুরুদেব, সেদিনকার সেই অকস্মাৎ ছিন্নবিচ্ছিন্ন অধ্যয়নসূত্র আর কি তেমন করিয়া জোড়া লাগিতে পারিল।”
ক্রমশ গুরুদেবও গৌরীর প্রতি আসক্ত হলেন। অন্যদিকে ঈর্ষাকাতর পরেশ জ্বালাযন্ত্রণায় ভুগে ইহজীবন ত্যাগ করল। পরেশের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে গুরুদেব পরমানন্দ যখন গৌরীর কাছে এসে তাকে নিয়ে যেতে চাইলেন গৌরী আত্মহত্যা করল। যে স্বামীকে সে ছেড়ে চলে যেতে চেয়েছিল তারই জন্য যেন সে সহমরণে গেল। আর যার কাছে সে যেতে চেয়েছিল সেই গুরুদেব পরমানন্দ যে মুহূর্তে লোভী হয়ে উঠলেন সেই মুহূর্তেই তাঁর অবস্থান গেল নেমে। স্খলিত হীন চেহারায় আত্মপ্রকাশ করা গুরুদেবকে তীব্র তীক্ষ্ণ প্রত্যাখ্যানও রইলো এই আত্মহননে। রবীন্দ্রগল্প সাধারণভাবে নারীর জীবনতৃষ্ণাকে মর্যাদা দেয়। যেখানে দিতে পারে না সামাজিক বাধ্যকতায়, সেখানেও এক অসহায় সুর ফুটে ওঠে। কিন্তু এই গল্পে যেভাবে এক সনাতনী চিন্তাকে উপসংহারে মান্যতা দেওয়া হল, তা আধুনিক পাঠককে বেশ অস্বস্তিতে ফেলে। নিরীক্ষাশীল ও দরদী রবীন্দ্রনাথের এ যেন প্রথাবদ্ধতার দিকে এক ক্ষণিকের পিছু হটা। আমাদের সৌভাগ্যকে এমন গল্প রবীন্দ্রনাথ তেমন একটা লেখেন নি। এই রকম দু একটি বিরল ব্যতিক্রম।
রবীন্দ্রনাথের অনেক গল্পেই কথক আমি নিজের নীচতা ও ক্ষুদ্রতাকে উন্মোচিত করে। দুর্বুদ্ধি গল্পের গল্পকথক ডাক্তার চরিত্রটিও তেমনই একজন। একদিকে সে চিকিৎসক, অন্যদিকে থানার দারোগার ঘনিষ্ট। থানার উল্টোদিকেই তার বাসা। এই যোগসাজস যে নানা অসাধু কাজ ও অর্থ উপার্জনে ব্যবহৃত হত, এই গল্পে তার ইঙ্গিৎ আছে। গল্পকথকের মেয়ে শশী যখন বিবাহের অনতি পরেই ওলাওঠায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেল, তখন তার সম্বিৎ ফিরল। নিজের কৃতকর্মের পাপের ফলেই কন্যাবিয়োগের যন্ত্রণা তাকে পেতে হল – এই ধারণাবশে তিনি আত্মধীক্কারে সামিল হলেন।
রবীন্দ্রনাথের উৎসর্গ কাব্যগ্রন্থের ৭ নম্বর কবিতার কয়েকটি লাইন আমাদের সবার অতি পরিচিত। “যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই,/যাহা পাই তাহা চাই না।” ফেল গল্পে কৌতুকের মধ্যে দিয়ে এই কথাটাই যেন বলা হয়েছে। নলিনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা তার বন্ধু নন্দর সঙ্গে। নলিন চায় নন্দের চেয়ে তার স্ত্রী সুন্দর হবে। সেজন্য সুদূর রাওয়ালপিণ্ডি প্রবাসী একজনের কন্যাকে আনানো হল কোলকাতায়। বিয়ের কথাবার্তা যখন এগোচ্ছে তখন খবর এলো নন্দের বিয়ের আয়োজনও পাকা। নন্দের বউয়ের খবর নিয়ে মনে হল সে বেশি সুন্দরী। নন্দকে জিততে দেওয়া যায় না। তাই টাকা ছড়িয়ে সেই মেয়েকেই নন্দের বিয়ে ভেঙে নিজের পাত্রী করল নলিন। এরপর নন্দের বিয়ে হল সেই রাওয়ালপিণ্ডির মেয়েটির সঙ্গেই। তখন নলিনের মনে হতে শুরু করল সে হেরে গেছে, কারণ সেই মেয়েটিই বোধহয় বেশি সুন্দরী ছিল।
ফেল গল্পটি আশ্বিন ১৩০৭ এ প্রকাশিত হয় ভারতী পত্রিকায়। ঐ মাসেই প্রদীপ পত্রিকায় বেরোয় শুভদৃষ্টি গল্পটি। এটির উপসংহার অনেকটাই যেন ফেল গল্পের বিপরীত। ফেল গল্পের শেষে নবীন যাকে বিয়ে করবে ভেবেছিল তার বদলে নিজে যেচে বিয়ে করল অন্য একজনকে এবং তারপর ভাবতে শুরু করল সিদ্ধান্ত ভুল হয়ে গেছে। শুভদৃষ্টি গল্পের নায়ক কান্তিচন্দ্র শিকারে গিয়ে একটি মেয়েকে দেখেন এবং তার রূপে মুগ্ধ হন। “মেয়েটির সৌন্দর্য নিরতিশয় নবীন, যেন বিশ্বকর্মা তাহাকে সদ্য নির্মাণ করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। বয়স ঠিক করা কঠিন। শরীরটি বিকশিত কিন্তু মুখটি এমন কাঁচা যে, সংসার কোথাও যেন তাহাকে লেশমাত্র স্পর্শ করে নাই”। এই রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হয়েই তিনি মেয়েটিকে বিয়ে করতে চান। গ্রামের গরীব ব্রাহ্মণ নবীন বাঁড়ুজ্যের বাড়িতে গিয়ে তাঁর মেয়েকে বিয়ে করার প্রস্তাব পেশ করলে তা সানন্দে অনুমোদিত হয়। বিয়ের পর বোঝা যায় নাম বিভ্রাটে শিকারকালে দেখা মেয়েটি তার বিবাহিত স্ত্রী নয়, এ অন্য কেউ। এখান থেকে কান্তিচন্দ্রেরও ফেল গল্পের নবীনের মতো ঠকে যাওয়ার আক্ষেপ শুরু হতে পারত। কিন্তু যখন জানা গেলে শিকারকালে দেখা মেয়েটির মুখ লাবণ্যে ভরা হলেও সে বোবা ও কালা, তখন ‘ভুল বিবাহ’কেই তার ভাগ্যগুণ বলে সে ধরে নিল।
এই সময়কালে বঙ্গদর্শন পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের দুটি গল্প বেরোয়। প্রথমটি দর্পহরণ। দাম্পত্যে পুরুষতান্ত্রিকতার তৎকালীন স্বাভাবিকতা দিয়ে এই গল্পের শুরু, কিন্তু শেষটি একেবারে অন্যরকম। গল্প শুরুর পুরুষতান্ত্রিকতা অবশ্য প্রচলিত ছকের নয়। সেখানে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অত্যাচার নেই, ভালোবাসাই আছে। কিন্তু স্ত্রীজাতির বিদ্যাবুদ্ধি, বিশেষ করে সৃজনশীল লেখালিখির দক্ষতা সম্পর্কে সন্দেহে গল্পের কথক স্বামীটির মন পরিপূর্ণ। স্ত্রী বাড়িতে পড়াশুনো করে যখন লেখালিখি শুরু করলেন, আর সেই লেখার কদর হতে থাকল চেনা অচেনা মহলে, তখন হরিশচন্দ্র হালদার নামক কথক স্বামীটি উদ্বেল হয়ে উঠলেন। এই নিয়ে মৃদু কথা চালাচালিও হয়ে গেল আর ঠিক হল এক গল্প লেখা প্রতিযোগিতায় স্বামী স্ত্রী অবতীর্ণ হবেন। নানা ইংরাজী গল্পের প্লট মাথায় নিয়ে কথক স্বামীটি একটি গল্প খাড়া করলেন, কিন্তু বিজয়ী হয়ে প্রকাশিত হল স্ত্রী নির্ঝরিণীর গল্পটিই। এরপর স্বামীর চোখ খুলল। মনও। এল উদার দৃষ্টি। স্ত্রীকে ঈর্ষা করা ছেড়ে, স্ত্রী জাতির সৃজনশীলতা সম্পর্কে ভুল ধারণা সংশোধন করে তিনি স্ত্রীর লেখালিখির পৃষ্ঠপোষক হতে চাইলেন। এই গল্পের আর একটি ব্যতিক্রমী দিক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিয়ের পর গল্পকথকের স্ত্রীকে লেখাপড়া শেখানোর ভার নিয়েছিলেন তার শ্বশুর মশাই তথা কথকের পিতা। পুত্রের চেয়ে পুত্রবধূর বাংলা ভাষাজ্ঞান ও লেখার দক্ষতা বিষয়েও তিনি ছিলেন উচ্চকন্ঠ। এরকম শ্বশুর সেকালে বাস্তব জীবনে কজন ছিলেন বলা মুশকিল, কিন্তু গল্পসাহিত্যে তাকে এনে রবীন্দ্রনাথ একটি উজ্জ্বল আদর্শ স্থাপণ করেছেন, যা একইসঙ্গে মধুর ও অনুসরণযোগ্য।
বঙ্গদর্শন পত্রিকায় প্রকাশিত এই পর্বের দ্বিতীয় গল্পটি হল মাল্যদান। কৌতুকের কারুণ্যে বদলে যাওয়া অনবদ্য এই গল্পটি পাঠকমনে সৃষ্টি করে গভীর অভিঘাত। গল্পের প্রথম অংশে আমরা দেখি সহায় সম্বলহীন বালিকা কুড়ানি আশ্রয় পেয়েছে পটল আর তার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট স্বামী হরকুমারবাবুর সংসারে। সেখানে নবীন ডাক্তার যতীনের নিত্য যাতায়াত। কুড়ানিকে যতীনের ভাবি স্ত্রীর কল্পিত আসনে বসিয়ে পটল এক ঠাট্টার পরিবেশ তৈরি করেছিল। এই ঠাট্টার আসল চেহারা কুড়ানির সরল মন না বুঝলেও যতীন বিব্রত হত আর তার মধ্যেই পটল পেত আমোদ। কিন্তু একদিন দেখা গেল ঠাট্টার নির্মোক ভেঙে কুড়ানি সত্যিই যতীনকে মন দিয়ে বসেছে। তারপর কুড়ানি লজ্জায় পটলের বাড়ি ছাড়ল। রাস্তায় তাকে পাওয়া গেল অসুস্থ অবস্থায়। শেষমেষ যতীনের ওপর পড়ল তার চিকিৎসাভার। সে তাকে নিজের ঘরে নিয়ে এল। কিন্তু তখন কুড়ানির শেষ সময় উপস্থিত হয়েছে। জরুরী বার্তা পেয়ে স্বামীকে নিয়ে পটল এল সেখানে। মৃত্যুর আগে যতীন কুড়ানির হাত থেকে পড়ল বিবাহ মালাটি। যেন পূর্ণ করল তার শেষ ইচ্ছে। এরপরেই নিভে গেল কুড়ানির জীবনদ্বীপ। একটি বেদনাবাষ্প জেগে রইলো পাঠকের মনে।
ভারতী পর্বের রবীন্দ্র গল্পগুলির মধ্যে তো বটেই, রবীন্দ্রনাথের গল্পভুবনেই নষ্টনীড়ের জুড়ি মেলা ভার। সেটি নিয়ে আমরা এখানে আলোচনা করলাম না। স্বতন্ত্রভাবে তাই নিয়ে লিখব।