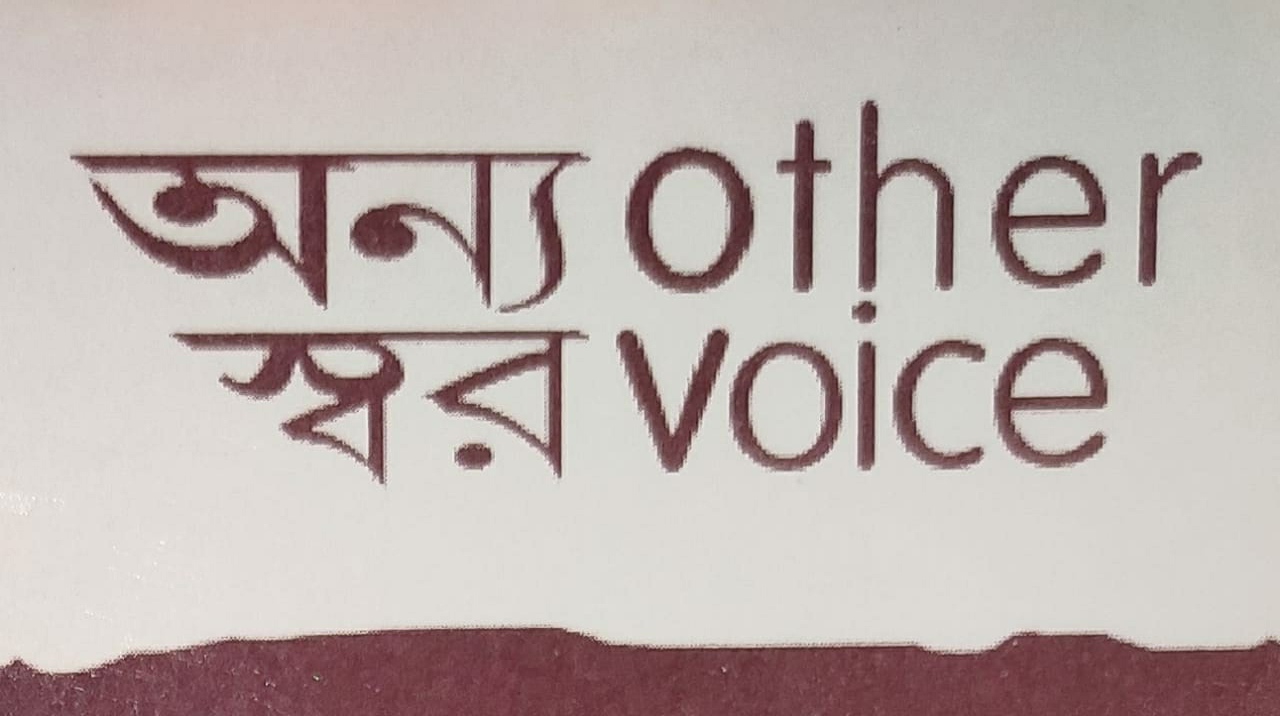সহজপাঠের সমাজমন
- 07 May, 2025
- লেখক: শ্রাবন্তী ঘোষাল
১৯৩০ সালের মে মাসে,বাংলা ১৩৩৭ সনে “সহজপাঠ” প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রকাশক ছিলেন জগদানন্দ রায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একই সাথে প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের খসড়া তৈরি করেন। শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ের শিশুদের বর্ণপরিচয় ও ভাষাশিক্ষার গোড়া-পত্তন পুস্তিকা (primar) হিসেবে বইটি লেখা হয়। ১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দের “The Pocket Book of Rabindranath Tagore এ পাওয়া সহজ পাঠের প্রথম খসড়ার পর, প্রায় চার দশক ধরে পান্ডুলিপি নির্মাণ করে বইটির প্রকাশ নিয়ে কবি স্বয়ং খুব আগ্রহী ছিলেন।প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ যিনি বিশ্বভারতীর গ্রন্থনবিভাগের প্রথম নির্দেশক ছিলেন, তাঁকে ১৪ই ভাদ্র,১৩৩৫ এ চিঠিতে তিনি লেখেন, ”সহজ পাঠ ছাপা হতে আর কত দিন দেরি?”
সহজ পাঠ প্রকাশের আগে রবীন্দ্রনাথ পাঠ্যপুস্তক হিসেবে সংস্কৃতশিক্ষা (১৮৯৬), ইংরাজি সোপান(১৯০৪), ইংরাজি শ্রুতিশিক্ষা(১৯০৯), ইংরাজি পাঠ(১৯০৯), ছুটির পড়া (১৯০৯), পাঠ সঞ্চয়(১৯১২), বিচিত্র পাঠ(১৯১৫), অনুবাদ চর্চা (১৯১৭), ইংরাজি সহজ শিক্ষা (১৯২৯) রচনা করেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে শান্তিনিকেতনে ১৯০১ সালে ব্রক্ষ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠার আগে ১৮৯৮-১৮৯৯ সময়কালে শিলাইদহে নিজের সন্তানদের পড়ানোর জন্য রবীন্দ্রনাথ একটি গৃহ বিদ্যালয় শুরু করেন।
বাংলা ভাষা শিক্ষায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের “বর্ণ পরিচয়” প্রথম ও দ্বিতীয়ভাগ ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশের ঠিক পঁচাত্তর বছর পর রবীন্দ্রনাথের “সহজ পাঠ” প্রকাশিত হয়।এই দীর্ঘ ব্যবধানে ঔপনিবেশিক রাজনীতির প্রভাবে সমাজ জীবনে ঘটে গেছে অনেক পরিবর্তন। ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দের বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব ও তার বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা জনআন্দোলনের পুরোধা পুরুষ রবীন্দ্রনাথের মনোজগতে বঙ্গ একান্তই যুক্তবাংলা।তাই ঢাকা থেকে আশাদাদা আসে।ছুটিতে কেউ বা যায় ত্রিবেণী, কেউ বা আত্রাই, কেউ বা উশ্রী নদীর ধারে। বক্সীগঞ্জের পদ্মাপারে হাট বসে,উল্লাপাড়ার মাঠ,আর্মেনি গির্জার ধারের মহানগরী কলকাতার অফিস সবই অবিভক্ত বাংলার মিলিত রূপ তুলে ধরে।শিশু মনে ভাষাভিত্তিক জাতি সংস্কৃতির সমৃদ্ধির ধারণা গড়ে ওঠে।
দেখি যে ছুটির ছবি:
“জীবনস্মৃতি”তে নিজের শৈশবের স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে কবি বলছেন,
‘একবার কলিকাতায় ডেঙ্গুজ্বরের তাড়ায় আমাদের বৃহত্ পরিবারের কিয়দংশ পেনেটিতে ছাতুবাবুদের বাগানে আশ্রয় লইল৷ আমরা তাহার মধ্যে ছিলাম৷ এই প্রথম বাহিরে গেলাম৷ গঙ্গার তীরভূমি যেন কোন পূর্বজন্মের পরিচয়ে আমাকে কোলে করিয়া লইল৷’ ১২৭৯ বঙ্গাব্দের গ্রীষ্মকালে কলকাতায় ডেঙ্গুজ্বরের প্রকোপ হলে অনেক সম্পন্ন পরিবারের মতোই ঠাকুর পরিবার পানিহাটির গঙ্গার ধারের একটি বাগানবাড়িতে কিছুদিন কাটান। বালক রবির সেই ছিল প্রথম ‘বাহিরে যাত্রা’, যখন তার বয়স এগারো বছর। বাংলার পল্লি ও প্রকৃতির সঙ্গে প্রথম পরিচয়৷ সহজ পাঠের প্রথম দুই খন্ড জুড়ে বেড়াতে যাওয়ার আকুতি;কখনো বা বেরিয়ে পড়া স্টিমারে,পালকিতে, নৌকায়, হেঁটে বা নিতান্তই মানসভ্রমণ। সহজ পাঠ প্রথম ভাগের নবম পাঠে গৌর নৌকা করে গৌরীপুর থেকে এল। পৌষ মাসে সে নৈহাটি যাবে। ঔ-কারের প্রয়োগ শেখার শেষে কবিতায় অনির্দিষ্টের পানে বেরিয়ে পড়ার আকুতি শোনা যায়।
“জানি না কোন্ দেশে পৌঁছে যাবে শেষে,
সেখানেতে কেমন মানুষ
থাকে কেমন বেশে!
থাকি ঘরের কোণে, সাধ জাগে মোর মনে—
অমনি করে যাই ভেসে ভাই,
নতুন নগর বনে।
দূর সাগরের পারে জলের ধারে ধারে
নারিকেলের বনগুলি সব
দাঁড়িয়ে সারে সারে।
পাহাড়চূড়া সাজে নীল আকাশের মাঝে,
বরফ ভেঙে ডিঙিয়ে যাওয়া
কেউ তা পারে না যে।
কোন্ সে বনের তলে নতুন ফুলে ফলে
নতুন নতুন পশু কত
বেড়ায় দলে দলে।
কত রাতের শেষে নৌকো যে যায় ভেসে—
বাবা কেন আপিসে যায়,
যায় না নতুন দেশে?”
একই বইয়ের দশম পাঠ এবং শেষ পাঠ্য অধ্যায় নিম্নোক্ত পঙক্তি দিয়ে শেষ হচ্ছে যা একই ভাবনার উচ্চারণ।
“আমি ভাবি ঘোড়া হয়ে মাঠ হব পার
কভু ভাবি মাছ হয়ে কাটিব সাঁতার
কভু ভাবি পাখি হয়ে উড়িব গগনে
কখনো হবে না সেকি ভাবি যাহা মনে।”
“সহজ পাঠ” দ্বিতীয় ভাগের একাদশ পাঠে বিনু এক রাতে স্বপ্ন দেখে কলিকাতা শহর নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছে। স্কুল,অঙ্কের বই,ব্যাকরণ হনহনিয়ে ছুটে চলেছে:সাথে ছোটে হাওড়া ব্রিজ,হ্যারিসন রোড,ট্রামলাইন। বারবার থামতে বলা সত্ত্বেও তার কোন হেলদোল নেই।এভাবে চলতে চলতে পুবের মানুষ, পশ্চিমে গিয়ে ঠেকলেও কোন আক্ষেপ নেই।কলকাতা,লাহোর, দিল্লি, আগ্রা শুধুই নাম।তাই স্বপ্নে তাদের ঠাঁই বদল করার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হলেও ঘুম ভেঙে বিনু কলাকাতাকে কলাকাতাতেই খুঁজে পায়।
“আমি মনে মনে ভাবি, চিন্তা তো নাই,
কলিকাতা যাক-নাকো সোজা বোম্বাই।
দিল্লি লাহোরে যাক, যাক-না আগ্রা,
মাথায় পাগড়ি দেবো, পায়েতে নাগ্রা।
কিম্বা সে যদি আজ বিলাতেই ছোটে
ইংরেজ হবে সবে বুট-হ্যাট-কোটে।
কিসের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল যেই,
দেখি কলিকাতা আছে কলিকাতাতেই।”
ঊনবিংশ শতকের শেষ ভাগ থেকেই বাঙালির বেড়ানোর সাথে পশ্চিমের যোগ নিবিড়।এ পশ্চিম ভূগোলকের সুদূর পশ্চিম নয়। নেহাতই বাংলার পশ্চিম দিকে বর্তমান বিহার ও ঝাড়খণ্ডের মালভূমি অঞ্চল। ”সহজ পাঠ” দ্বিতীয় ভাগের ষষ্ঠ পাঠে উস্রি নদীর ঝর্ণা দেখতে যাওয়ার প্রস্তুতি চলে। শ্রাবণ মাসের বাদলায় কলেজের দু'দিন ছুটিতে বেড়াতে যাওয়া হচ্ছে।পথের খাবার হিসেবে নেয়া হচ্ছে সন্দেশ,পান্তোয়া,বোঁদে আর সাথে যাচ্ছে কান্ত চাকর। সপ্তম পাঠে এই পরিকল্পনা আরো বিস্তৃত হচ্ছে। শ্রীশকে দিয়ে বসন্তের দোকানের খাস্তা কচুরী আর পেস্তা বাদাম আনানো হবে। রাস্তায় রেঁধে খাওয়ার ব্যবস্থার জন্য সাথে নেয়া হবে কড়া,খুন্তি,জলের পাত্র আর আস্ত কাৎলা মাছ,আলু বা তার পরিবর্তে ওল।
সহজ পাঠের দ্বিতীয় ভাগের একাদশ পাঠে আছে শিকারের গল্প।বিপ্রগ্রামের বাঘ মারার জন্য শক্তিবাবু তার ‘'রক্তজবা’ নৌকায় আক্রম সিংকে সঙ্গী করে শিকারে চললেন। তিনি খেলেন লুচি,আলুর দম আর পাঁঠার মাংস আর আক্রম সিংহের খাদ্যাভ্যাস ‘'পশ্চিমি”। সে খায় রুটি দিয়ে চাটনি। কাহিনীর শেষে জানা যায় পথ হারানো শক্তিবাবুকে কাঠুরিয়ারা যত্ন করে তালপাতার ঠোঙায় চিঁড়ে,বনের মধু আর ছাগলের দুধ খাইয়েছে। দিনের শেষে তাকে নৌকায় পৌঁছিয়ে দেয়ার পর তিনি দশ টাকা বখশিশ দিতে চাইলে কাঠুরিয়া সর্দার করজোড়ে তা ফিরিয়ে দিয়ে বলেছে,”মাপ করবেন,টাকা নিতে পারব না,নিলে অধর্ম হবে”। ঘরের বাইরেও যে, আপ্যায়ন, আতিথেয়তা, উষ্ণতা অপেক্ষা করে থাকে এবং তা লাভ করা যে বেড়াতে যাওয়ার অন্যতম প্রাপ্তি শিশুমনে এই ছবি থেকে যায়।
বাস্তবে বেড়ানোর সুযোগ না ঘটলেও মনে মনে তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে পক্ষীরাজে চড়ে নদীর ধারের ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীকে পথ শুধিয়ে নিয়ে রাজার বাড়ি পৌঁছে যাওয়া সম্ভব।
চেয়ে চেয়ে চুপ ক’রে রই—
তেপান্তরের পার বুঝি ওই,
মনে ভাবি ঐখানেতেই
আছে রাজার বাড়ি।
থাকতো যদি মেঘে-ওড়া
পক্ষিরাজের বাচ্ছা ঘোড়া
তক্ষনি-যে যেতেম তারে
লাগাম দিয়ে ক’ষে,
যেতে যেতে নদীর তীরে
ব্যঙ্গমা আর ব্যাঙ্গমীরে
পথ শুধিয়ে নিতেম আমি
গাছের তলায় ব’সে।
(সহজ পাঠ,দ্বিতীয় ভাগ,নবম পাঠ)
তেমনি গোপন দুয়ার খুলে ফুলের রাজ্যে চলে যাওয়া যায় যেখানে গোপন দুয়ার খুলে নানা রঙের মেঘেরা আসা যাওয়া করে।
“ওদের সে ঘর খানি
থাকে কি মাটির কাছে?
দাদা বলে, জানি জানি
সে ঘর আকাশে আছে।
সেথা করে আসা যাওয়া
নানারঙা মেঘ গুলি।
আসে আলো, আসে হাওয়া
গোপন দুয়ার খুলি।”
(সহজ পাঠ,প্রথম ভাগ,সপ্তম পাঠ)
“স্টিমার আসিছে ঘাটে”
রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কালে জলপথ মূল যোগাযোগের মাধ্যম ছিল।বিশেষত কলকাতা থেকে পূর্ব বাংলায় এবং দক্ষিণবঙ্গে নদী,খাল ইত্যাদির আধিক্য এবং বর্ষার জলে বন্যার জন্য জলপথে সমাজের সব স্তরের মানুষ অধিকাংশ ক্ষেত্রে নৌকা বা স্টিমার ব্যবহার করতেন। এমনি এক স্টিমার ঘাটের কথা সহজ পাঠ দ্বিতীয় ভাগের দ্বাদশ পাঠের কবিতায় স্থান পেয়েছে। দূর দেশ থেকে কলকাতা শহরে কাজে আসা মানুষজন পূজার ছুটির আগে বাড়ি ফিরছে। শত শত মালপত্রের ভীড়ে,মানুষের প্রবল ঠেসাঠেসির মাঝে হরেরাম হারমোনিয়াম বাজিয়ে জীবিকা নির্বাহ করছে। রেশমের জামা পরা কলকাতা থেকে আসা চন্ডী, অবিনাশের পাশে চিনে জুতো পরে মশমশিয়ে আসে বঙ্কু শ্যামদাস,অম্বিকা,অক্ষয়। কনুইয়ের গুঁতোয় ভীড় ঠেলে সবাই এগিয়ে চলে।হাতে ঘড়ি বাঁধা, চোখে চশমা,সরু ছড়ি হাতে অপেক্ষাকৃত শৌখিন বাবুদের পাশাপাশি স্টিমারে আছে মা এবং শিশু। নোঙর জলে ডুবে যাত্রা এবার শেষ হয়। জাহাজ শিকলে বাঁধা পড়ে। মালবাহকরা ঘাটে এসে জড়ো হন।আত্মীয় বন্ধুদের অপেক্ষায় যারা আসেন তাদের ডাকাডাকিতে ঘাট মুখরিত হয়ে ওঠে।ঘাট থেকে গোরুর গাড়ি,পালকি,ডুলিতে যাত্রীরা ঘরের পানে যায়।ক্রমশ সূর্য পাটে যায়।বেলা ফুরিয়ে সন্ধে নামে।কেরোসিন লন্ঠনের আলো অনুসরণ করে মাথায় মালপত্র বোঝাই করে মুটেরা পথ চলে।স্টিমার ঘাট ফাঁকা হয়ে আসে। দূরে শিয়াল ডাকে আর মুদির দোকানে টিমটিমে আলো জ্বলে।
১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে পারিবারিক জমিদারির দেখাশোনা করে তার আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাবার আদেশে রবীন্দ্রনাথ স্ত্রী, সন্তানদের সাথে নিয়ে শিলাইদহে আসেন। পদ্মাপারে সাজাদপুর পতিসর, শিলাইদহ জুড়ে নদীমাতৃক বিস্তৃত ভূখন্ডের পল্লীজীবন,কৃষি, প্রকৃতির অবারিত রূপ তার কাছে নতুন এক জগত খুলে দিয়েছিল। তিনি অধিকাংশ সময় তার একান্ত প্রিয় ‘'পদ্মা’ বোটে কাটাতেন।
'পদ্মাপ্রবাহচুম্বিত শিলাইদহ' থেকে ভাইঝি ইন্দিরা দেবীকে চিঠিতে লিখেছিলেন, 'পৃথিবী যে বাস্তবিক কী আশ্চর্য সুন্দরী তা কলকাতায় থাকলে ভুলে যেতে হয়। এই-যে ছোটো নদীর ধারে শান্তিময় গাছপালার মধ্যে সূর্য প্রতিদিন অস্ত যাচ্ছে, এবং এই অনন্ত ধূসর নির্জন নিঃশব্দ চরের উপরে প্রতি রাত্রে শত সহস্র নক্ষত্রের নিঃশব্দ অভ্যুদয় হচ্ছে, জগৎ-সংসারে এ-যে কী একটা আশ্চর্য মহৎ ঘটনা তা এখানে থাকলে তবে বোঝা যায়।'
প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়কে লেখা চিঠির সূত্রে জানা যায় ১৯৩৭ সালে কবি শিয়ালদহ থেকে ট্রেনে আত্রাই স্টেশনে এসে নদীপথে পতিসরে পৌঁছে যান।
১৯৩০ সালে সহজপাঠ প্রকাশের পূর্ব্ববর্তী বছরগুলোতে রবীন্দ্রনাথ বারবার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দেশে জাহাজ যাত্রা করেছেন। ১৯২৮ সালে প্রাচ্যের জাভা, বালি, কুয়ালালামপুর, পেনাং, সিঙ্গাপুর ইত্যাদি কয়েকটি দেশে তিনি জলপথে ভ্রমণ করেন।
১৯২৮ সালে অক্সফোর্ডের হিবার্ট বক্তৃতার জন্য আমন্ত্রিত হলেও দীর্ঘ ভ্রমণজনিত শারীরিক অসুস্থতার কারণে সেই আমন্ত্রণ গ্রহণে তিনি অপারগ হন। অবশেষে ১৯৩০ সালের ২রা মার্চ পুত্র রথীন্দ্রনাথ,পুত্রবধূ প্রতিমাদেবী সহ আরো কয়েকজনে বিশিষ্ট মানুষের সাথে জাহাজপথে ১৮ই মার্চ তিনি বিলেতে পৌঁছান।
সহজ পাঠের দ্বিতীয় ভাগের দ্বাদশ পাঠের কবিতায় মহাজনী নৌকার কথা পাওয়া যায়া।আশ্বিনে সম্ভবত উৎসবের আগে নানারকম পণ্যে বোঝাই মহাজনী নৌকা ঘাটে আসে।পশ্চিমি মাল্লাদের মাদল বাজানোর শব্দের পাশাপাশি ঘাট জুড়ে হাঁকাহাঁকি, ঠেলাঠেলির মহাশোরগোল কানে আসে। ক্রমশ বোঝা নিয়ে চলে যাওয়া ক্লান্ত গরুর গাড়ির চাকার শব্দ মিলিয়ে আসে। অন্ধ গায়কের কন্ঠের আগমনী গান শোনা যায়।
“আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে”
বাংলার মাঠ,ঘাট,নদী,গ্রাম,শহর বন্দর,ঝোপঝাড়, বনবাদাড়ের কথা সহজ পাঠের অন্যতম দেশজ সম্পদ। হুগলি জেলার গুপ্তিপাড়া,চন্দননগর, বরিশাল জেলার গৈলা, চব্বিশ পরগনার নৈহাটি, কুষ্টিয়ার উল্লাপুর, কলকাতা,ঢাকা কাঁটাতার এবং গ্রাম-শহর দ্বৈরথ মুক্ত এক পৃথিবী নির্মাণ করে।ছুটিতে কেউ বা বেড়াতে যায় ত্রিবেণী, কেউ বা আত্রাই। শিলং পাহাড়ের বন্যার জলে কর্ণফুলী নদীতে বন্যা হয়।নাম না জানা আঁকে বাঁকে চলা ছোটনদীর সাথে তিস্তা,আত্রাই,ইছামতী, উস্রির নাম পাওয়া যায়। সহজ পাঠ দ্বিতীয় ভাগের চতুর্থ পাঠে চন্দননগরের আনন্দ বাবু আসার কথা জানা যায়। তার জন্য মালা-চন্দনের পাশাপাশি অন্ধ গায়কের কন্ঠে বন্দেমাতরম গান শোনানোর প্রস্তুতি দেখা যায়।
আবার দ্বাদশ পাঠে গুপ্তিপাড়ার বিশ্বম্ভরবাবু ইস্টিমার ঘাটের ইস্টিশন বাবুর অম্লশূল চিকিৎসার জন্য পালকি চেপে বিষ্ণুপুর যাত্রা করেন। স্বর্ণগঞ্জের পদ্মার চরে তারা রান্না করে খাবার খান। পথে তিল্পনি খাল পার হলে ডাকাতদল তাকে আক্রমণ করে।উল্লাপাড়ার মাঠ, শেয়ালের দল, উচ্ছে গাছের ঝিঁঝিপোকা, অশ্বত্থ গাছে পেঁচা, বাঁশবাগানের মাথায়, তেঁতুল ডালের পাতায় ঝুমকো ফুলের লতা, বাঁশবনের ডালে ঝিলমিলিয়ে ওঠা রোদ বঙ্গপ্রকৃতির চেনা স্নিগ্ধ রূপ মেলে ধরে। ঝুমকো ফুলের লতা হারিয়ে পাওয়া আলোটিকে নাচিয়ে দিয়ে যায়। রান্নাঘরের চালে তিনটে শালিকের ঝগড়া, শীতের দুপুরে বেগুনী শাড়ি রোদে দেওয়া বালিকা, বোষ্টমী,অবিনাশের ঘাস কাটা, ডিঙিতে আসা চাষী আর প,ফ,ব,ভ এর ধান কাটা (“প,ফ,ব,ভ যায় মাঠে, সারাদিন ধান কাটে), খালে বকের মাছ ধরা, তালবনের ভেতর দিয়ে পথ, আমলকী বনের পাতা খসানো, তিল-তিসির ক্ষেত - সবই এক ক্যানভাসে উঠে আসে।
উদ্ভব মন্ডলের মেয়ের বিয়েতে গ্রামের জমিদারের পিসি কাত্যায়নী সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। কায়িক শ্রম নির্ভর কৃষি সভ্যতায় আর্থিক ভাবে সচ্ছ্বল যারা তারা হরিগানের গায়ক,অন্ধ ভিখারি, বোষ্টমীকে ফিরিয়ে দেন না।
“গাড়ি চালায় বংশীবদন”
গ্রামজীবনের অন্যতম ক্রয়-বিক্রয় কেন্দ্রা এবং রীতিমতো আকর্ষণীয় বেড়াতে যাওয়ার জায়গা হলো হাট।”সহজ পাঠ “ প্রথম ভাগের “হাট” কবিতায় গরুর গাড়ির চালক বংশীবদনের ভাগনে মদন মামার অনুগামী হয়ে রীতিমতো গর্বিত।অনেকটা তার চোখ দিয়েই হাটের সাথে আমাদের পরিচয় ঘটে।কেনাকাটার বিপুল আয়োজনে পটল,বেগুন,মুলো ইত্যাদি সবজি,সর্ষে,ছোলা,ময়দা,আটা,বেতের কুলো-ধামা,এখো গুড় এসব কৃষিজ পণ্যের সাথেই আছে শহর থেকে আসা সস্তা ছাতা,শীতের র্যাপার, ঝাঝঁরি হাতা। শুধু বালক বা কিশোর বংশীবদন নয়, চাষীর মেয়েও খড়ের আঁটি বোঝাই করে নৌকা চালিয়ে হাটে আসে।
একই বইয়ের তৃতীয় পাঠে দাদা আর মামা হাটে যায়।ছানা,গজা,খাজা কিনে আনার ফরমায়েশ থাকে।চাল,ডাল,আটার সাথে কেনা হয় আতা,আখ,জাম আর শাক।
“যাই শহরের দিকে চলে”
ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক শাসনের সুবাদে শহর ক্রমশ মহানগরে পরিণত হয়। নগরায়নের ফলে গ্রাম থেকে শহরে কাজের জন্য মানুষের আনাগোনা বেড়ে চলে।ইংরাজি জানা কেরাণি তৈরীর শিক্ষাব্যবস্থার প্রসারের ফলে অফিস-আদালত ছাড়াও কায়িক শ্রমের জন্য শহরে বিপুল কাজের ক্ষেত্র তৈরী হয়। “সহজ পাঠ” দ্বিতীয় ভাগের সপ্তম পাঠের কবিতায় তমিজ মিঞার গরুর গাড়ি চড়ে যে সহজে যায় সে দেয়াল গাঁথে,ছাত “পিটোয়”।সারাদিনে বাসনওয়ালা-আতাওয়ালার সুর করে হাঁক,গাড়ি-ঘোড়ার শব্দ শোনা যায়।বিকেল সাড়ে চারটের পর রোদ পড়ে এলে ভারা থেকে নেমে এসে শ্রমিক গ্রামের পুকুর পাড়ের গাজন-তলার বাঁয়ের নিজের ঘরে ফিরে আসেন।
অষ্টমপাঠে আর্মেনি গির্জার কাছে অফিসের কথা জানা যায়।বাদলা দিনে অফিসের ভাত খেয়ে বাবু সেই পথে যাবেন।চতুর্থ পাঠে চন্দননগরের আনন্দ বাবুর আসার কথা জানা যায়। তৃতীয় পাঠে পাড়ার জঙ্গল সাফ করার দিনে মোটরগাড়ির কথা প্রথম জানা যায়।রঙ্গলাল বাবু আর তার দাদা বঙ্গবাবুকে আনার জন্য রঙ্গলালের মোটরগাড়ির প্রসঙ্গ আসে।
“হোথায় হব বনবাসী “
শহর,গ্রাম,তেপান্তর কোথাও স্বস্তি না পেলে মাকে নিয়ে জিয়ল গাছের বেড়ার ধারে কুঁড়েঘর তৈরী করেমানুষের সভ্যতা থেকে অব্যাহতি নিয়ে বনবাসী হ'বার সাধ জাগে।ঝাউতলার কুঁড়েঘরের পাহারায় থাকা শিশু রাক্ষস,বাঘ,ভাল্লুকের সাথে ধনুক হাতে লড়তে চায়। বনের হরিণ মায়ের পায়ের কাছে খই খেতে আসবে।ফলসাবনের কাছে ময়ূর এসে নাচ দেখিয়ে যাবে।শালিখ,কাঠবেড়ালির সমাগমে মুখরিত হবে বন।
“” শালিখেরা সব মিছিমিছি
লাগিয়ে দেবে কিচিমিচি,
কাঠবেড়ালি লেজটি তুলে
হাত থেকে ধান খাবে”
(সহজ পাঠ,দ্বিতীয় ভাগ,পঞ্চম পাঠ)
এই বইয়ের একাদশ পাঠে শক্তিনাথ বাবু তার নৌকা চড়ে বাঘ শিকার করতে বেরিয়েছিলেন। জনপ্রাণীহীন ঘন জঙ্গলে ছোট সোঁতার ধারে গাছের গুড়িতে বাঘের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। বিজলি বাতির মশাল দেখে বাঘ দৌড়ে পালিয়ে যায় কিন্তু জঙ্গলের মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলে কাঠুরিয়াদের যত্ন ও আতিথ্যে তারা সুস্থ দেহে নৌকায় ফিরে আসেন। সহজপাঠের জল জঙ্গল পারস্পরিক বন্ধনের এক প্রাণজ সত্ত্বা।
সহজপাঠের সহজ জীবনের ছবিতে ছোট ছোট আনন্দের রেশ,নতুন জায়গায় বেড়ানোর আনন্দ,স্থান বিশেষের বৈশিষ্ট্য,স্টীমার-পালকি,গরুর গাড়ি-ট্রাম পাঠকের বা শিক্ষার্থীর কাছে নিত্য নতুন চমক নিয়ে আসে। অবিভক্ত বাংলার গ্রাম,গঞ্জ,শহর,স্টিমার ঘাট,নদীর ধার,জঙ্গলের পথ জূড়ে যে দীর্ঘ পথ তৈরী হয় তা অনুসরণ করে কল্পলোকে এক দেশের ছবি এঁকে চলে শিশু মন। যে পথ সকল দেশ পেরিয়ে উদাস হয়ে কোথায় যেন হারিয়ে যায়। দূরবর্তী কোন দেশের দূর-দূরান্তে মন ঘুরে বেড়ায় যেখানে হারিয়ে যেতে কোন মানা নেই।