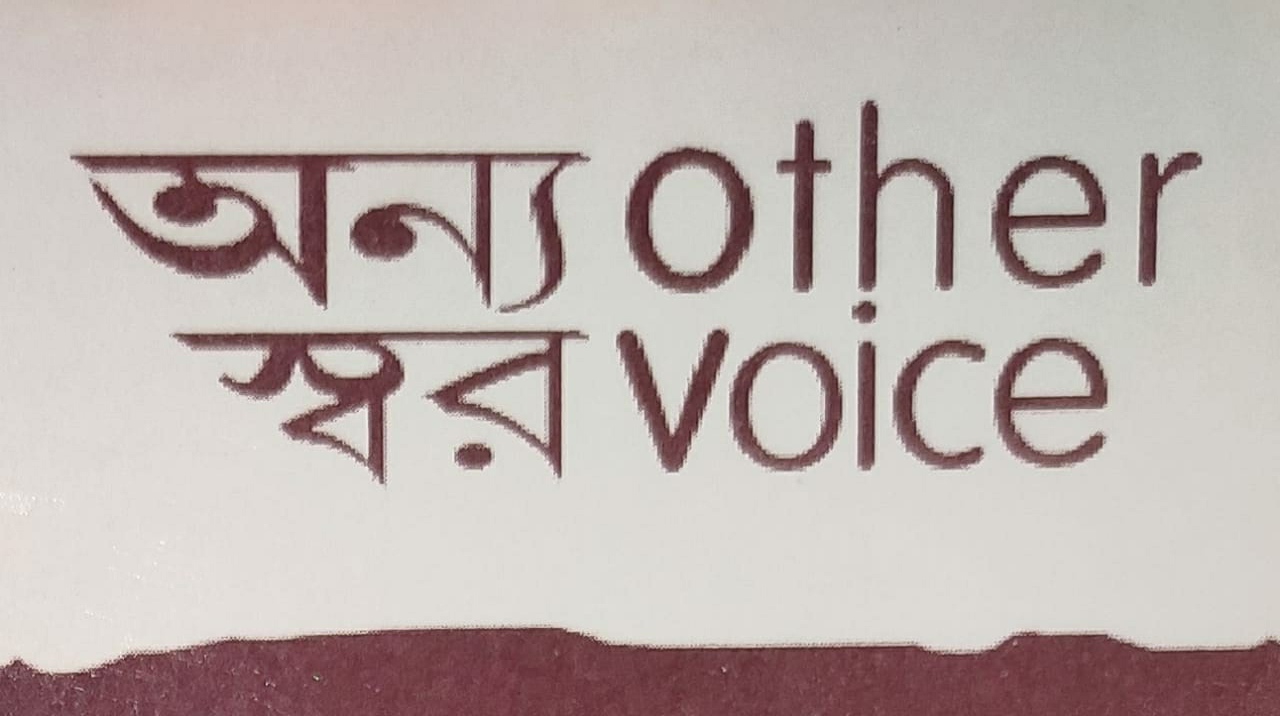রবীন্দ্রনাথের তিনসঙ্গী
- 07 May, 2025
- লেখক: সৌভিক ঘোষাল
প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কালে ইউরোপের শিল্প সাহিত্যে যে নতুন আধুনিকতার জন্ম হয়েছেল, তা বিশ্বের নানা জায়গার মতো বাংলার সাহিত্য সংস্কৃতিকেও প্রভাবিত করেছিল প্রবল পরিমাণে। নতুন সময়ে বস্তুজগৎ ও চিন্তার জগতেও এসেছিল ব্যাপক রদবদল। এই পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথও মহাযুদ্ধোত্তরকালে তাঁর সাহিত্যে ভাঙচুর ঘটিয়েছেন প্রচুর। সেই ভাঙচুরের মধ্যে দিয়ে তিনি জীবন সায়াহ্নে এসে পৌঁছলেন তিনসঙ্গীর গল্পগুলিতে। এই গল্পগুলির মধ্যে কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। স্বতন্ত্র আলোচনায় যাবার আগে সে দিকে একটু তাকানো যাক।
তিনটি গল্পেই আমরা এমন নায়িকাদের পাই, যারা সংস্কার মুক্ত দেশ দুনিয়ার খবর রাখে। শেষকথার রুচিরা বা রবিবারের বিভা নিজেরা যে খুব ঐতিহ্য বা শিকড় ছিঁড়ে বেরিয়ে এসেছে তা নয়, তবে তাঁদের আশেপাশে উপস্থিত এমন মেয়েদের কথা তারা জানে। এমন অনেকের কথা রবিবার গল্পে এসেওছে। আর ল্যাবরেটরি গল্পের দুই নায়িকা, মা ও মেয়ে, সোহিনী ও নীলা তো ট্রাডিশনাল নারী আর্কেটাইপের পুরোপুরি বাইরেই অবস্থিত। তারা, বিশেষ করে সোহিনী এতটাই আলাদা, যে রবীন্দ্রনাথ তাকে বাঙালি মেয়ে হিসেবে না গড়ে পাঞ্জাবী মেয়ের পরিচয়ে গড়েছেন। হয়ত ভেবেছেন বাঙালি মেয়ের এই চরিত্রনির্মাণ পাঠকের বিশ্বাস উৎপাদনে ব্যর্থ হবে। তিনটি গল্পে যে সমস্ত উল্লেখযোগ্য পুরুষের দেখা আমরা পাই তারা সবাই বিজ্ঞান বা শিল্পকলার নিবিষ্ট সাধক, জ্ঞানজগতের উচ্চমার্গে তাঁদের বিচরণ। তাঁদের কেউ কেউ উচ্চ ডিগ্রী ও গবেষণা অভিজ্ঞতা নিয়ে বিলেত ফেরৎ, যেমন শেষকথার ডক্টর নবীনমাধব সেনগুপ্ত বা আচার্য ডক্টর অনিল কুমার সেনগুপ্ত। কেউ কেউ সেখানে যাবার সুযোগ পেয়েছে কিন্তু বাড়ির অমত থাকায় যেতে পারে নি, যেমন ল্যাবরেটরির রেবতী, কেউ বা আবার নিজেকে প্রমাণ করতে সেখানে যেতে চলেছে, যেমন রবিবার গল্পের অভীক বা অমরবাবু। জীবন্ত চরিত্র হিসেবে ল্যাবরেটরি গল্পে নন্দকিশোর উপস্থিত না থাকলেও আদ্যন্ত তিনি এ গল্পে ছায়া ফেলেছেন প্রয়াণ পরবর্তী নানা স্মৃতিচারণা ও আলোচনায়। গল্পের প্রথম বাক্যেই তাঁর সম্পর্কে কথক আমাদের জানিয়ে দেন, “নন্দকিশোর ছিলেন লণ্ডন য়ুনিভার্সিটি থেকে পাস করা এঞ্জিনীয়ার। যাকে সাধুভাষায় বলা যেতে পারে দেদীপ্যমান ছাত্র অর্থাৎ ব্রিলিয়ান্ট, তিনি ছিলেন তাই। স্কুল থেকে আরম্ভ করে শেষ পর্যন্ত পরীক্ষার তোরণে তোরণে ছিলেন পয়লা শ্রেণীর সওয়ারী।”
তিনসঙ্গীর তিনটি গল্পই এক অর্থে প্রত্যাখ্যানের গল্প। রবিবার আর শেষকথার প্রত্যাখ্যানগত মিল বেশি, ল্যাবরেটরি খানিকটা অন্য ধরনের। রবিবার গল্পে বিভা অভীককে আর শেষকথা গল্পে রুচিরা নবীনমাধবকে ফিরিয়ে দেয়, কারণ দুই নায়িকাই মনে করেছিল ভালোবাসার মানুষদের কাছে ধরা দিলে সেই প্রতিভাবান মানুষগুলি আকাশ থেকে নীড়ে বাঁধা পড়বে, তাদের সারস্বতকর্মে বিঘ্ন হবে সংসারধর্ম। তাই তাদের সম্মান করে, ভালোবেসে, যন্ত্রণাবিদ্ধ হয়েও পাশে সরে দাঁড়ানো ভালো। ল্যাবরেটরি গল্পে রেবতীকে নীলা অবশ্য বিয়ে করতে উদ্যত হয়েছিল, কিন্তু নীলার মা সোহিনী যখন দেখলেন নীলাকে বিয়ে করলে রেবতী নিজেও ডুববে আর তার ও প্রয়াত স্বামীর স্বপ্নসৌধ ল্যাবরেটরিটিরও সর্বনাশ হবে, তখন তিনিই একদা জামাই হিসেবে পছন্দ করা রেবতীকে বিবাহ উদ্যোগ থেকে সবলে দূরে সরিয়ে দিলেন।
তিনটি গল্পেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর আগের পর্বের, বিশেষ করে হিতবাদী সাধনা ভারতী পর্বের ছোটগল্পের প্যাটার্ন থেকে সরে এসেছেন। আগের পর্বের রবীন্দ্র গল্প মূলত গড়ে উঠেছিল গ্রামীণ পটভূমিকায়, তার ভাষা সংলাপ চরিত্র কাহিনী সবকিছুই ছিল জল মাটি হৃদয়ের কাছাকাছি। তিনসঙ্গীর গল্পগুলি চরিত্রে নাগরিক, সেখানে রয়েছে বুদ্ধি ও স্মার্টনেসের দীপ্তি। আকর্ষণ বিকর্ষণের নাটকীয়তা, প্রত্যাশ্যা প্রত্যাখ্যানের মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব, চিন্তার দীপ্তি, সংলাপ ও বর্ণনার উজ্জ্বলতা কীভাবে তিনসঙ্গীর গল্পগুলিকে বিশিষ্ট করে তুলেছে, তা বুঝতে এগুলির স্বতন্ত্র ও বিস্তারিত আলোচনার দিকে এবার এগনো দরকার।
রবিবার
রবিবার গল্পের নায়ক অভীক নাস্তিক, দার্শনিক পরিভাষায় বললে নিরীশ্বরবাদী, সেই নিরীশ্বরবাদ শুধু নিজের মতাদর্শ হয়েই ছিল না, তা বিশ্বাসী মনকে আঘাত করতেও উদ্যত হয়েছিল। ঠাকুরঘরে কোনও এক মহা অনর্থ ঘটনার পর তার বাবা তাঁকে ত্যাজ্যপুত্র করেন। বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার সময় মা তার হাতে টাকা দিতে চাইলেও তাঁর আত্মমর্যাদা বোধ তাকে সে টাকা নিতে দেয় নি। বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে এক কাপড়ে। গল্পকথক আমাদের জানিয়েছেন অভীকের বাল্যকাল থেকেই দুটি বিষয়ে আগ্রহ ছিল – ছবি আঁকা ও যন্ত্রবিদ্যা। “জীবনে ওর দুটি উলটো জাতের শখ ছিল, এক কলকারখানা জোড়াতাড়া দেওয়া, আর-এক ছবি আঁকা। ওর বাপের ছিল তিনখানা মোটরগাড়ি, তাঁর মফস্বল-অভিযানের বাহন। যন্ত্রবিদ্যায় ওর হাতেখড়ি সেইগুলো নিয়ে। তা ছাড়া তাঁর ক্লায়েন্টের ছিল মোটরের কারখানা, সেইখানে ও শখ ক'রে বেগার খেটেছে অনেকদিন।” বাড়ি ছাড়ার পর মোটর মিস্ত্রীর পেশা বেছে নিয়ে কষ্টকর দিন যাপন করেছে সে। বেশ কিছু টাকা জমার পর ফিরে গেছে নেশা ছবি আঁকার কাছে।
অভীক চিন্তাচেতনায় যেমন বাঁধা গৎ ভাঙাতে উৎসাহী, তেমনি আর্টের ক্ষেত্রেও নতুন পথের পথিক। কথক আমাদের জানাচ্ছেন, “অভীক ছবি আঁকা শিখতে গিয়েছিল সরকারী আর্টস্কুলে। কিছুকালের মধ্যেই ওর এই বিশ্বাস দৃঢ় হল যে, আর বেশিদিন শিখলে ওর হাত হবে কলে-তৈরি, ওর মগজ হবে ছাঁচে-ঢালা। ও আর্টিস্ট, সেই কথাটা প্রমাণ করতে লাগল নিজের জোর আওয়াজে। প্রদর্শনী বের করলে ছবির, কাগজের বিজ্ঞাপনে তার পরিচয় বেরল আধুনিক ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ আর্টিস্ট অভীককুমার, বাঙালি টিশিয়ান।” তার আশেপাশে থাকা বান্ধবীকুল তার প্রেমে মাতয়ারা হয়ে তার ছবিকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেও অভীক জানত এরা শিল্পবোদ্ধা নয়, ছবিকে ভালোবেসে তারা এসবের প্রশংসা করছে না। তাদের স্তুতি আসলে ব্যক্তি অভীককে মুগ্ধ করার জন্য। এই অন্তঃসারশূন্য স্তুতিবাক্য কোনও শিল্পীকে মুগ্ধ করতে পারে না। অভীককেও পারে নি। পরিচিতবৃত্তের তোষামোদী বাক্যের বাইরে তার ছকভাঙা ছবির কদর এদেশে তেমন হল না। সে মনে করল এদেশে পরম্পরাকে ভেঙে নিজস্বতা প্রকাশের জায়গা তেমন নেই, তার ছক ভাঙা ছবির স্বীকৃতি আসতে পারে কেবল ইউরোপের শিক্ষিত জনসমাজ থেকেই। তাই সেখানে যাবার জন্য সে ব্যাগ্র হয়ে উঠল। “আমাদের এই চোখে-ঠুলি-পরা ঘানি-ঘোরানোর দেশে আমার চলবে না। যাদের দেখবার স্বাধীন দৃষ্টি আছে, আমি যাবই তাদের দেশে।”
ছবির ক্ষেত্রে যেমন বান্ধবীকুলের অন্তঃসারশূন্য প্রশস্তি অভীককে খুশি করতে পারে নি, তেমনি তাদের গায়ে পড়া মুগ্ধতার মধ্যেও সে প্রকৃত ভালোবাসা খুঁজে পায় নি। যৌবনের উত্তাপে তাদের সঙ্গে উন্মুক্ত মেলামেশা করলেও সেখানে তার প্রাণের আরাম, মনের শান্তি ছিল না। সে ভালোবেসেছিল বিভাকে তাকেই সমর্পণ করতে চেয়েছিল মনপ্রাণ। হয়ত বিভার মনে ঈর্ষাজ্বালা প্রকট করে তাকে আকর্ষণ করার জন্যই সে বান্ধবী সংসর্গের কথা বেশ জাঁক করে বিভাকে জানাত। শীলাকে নিয়ে ক্রাইসলার গাড়িতে ঘোরার ইচ্ছে জানানোর মধ্যে এমন অভিপ্রায় লুকিয়ে থাকা অসম্ভব নয়। কিন্তু অভীককে ভালোবেসেও বিভা তার সঙ্গে বন্ধনে জড়িয়ে পড়তে চায় নি। তিনসঙ্গীর তিনটি গল্পের কেন্দ্রেই আছে একটি করে প্রত্যাখ্যান। রবিবার গল্পের কেন্দ্রকটি তৈরি হয়েছে বিভার তরফে অভীককে প্রত্যাখ্যানের মধ্যে দিয়ে।
প্রশ্ন উঠতে পারে কেন এই প্রত্যাখ্যান? বিভা যে অভীককে ভালোবেসেছিল, তাতে তো কোনও সন্দেহ নেই। এই প্রত্যাখ্যানের পেছনে বাইরের কোনও কারণ, যেমন অভীকের খোলামেলা বহুনারী সঙ্গও বাধা হয়েছিল বলে মনে হয় না। কারণ সমাজরটনা যাই থাকুক, বিভা অভীকের এই ভ্রমরবৃত্তিকে চরিত্রের মৌলিক দোষ হিসেবে ভেবেছিল বলে মনে হয় না। অভীক যে এইসব সংসর্গের গল্প তার কাছে জাঁক করে বলে তার মধ্যে ঈর্ষা জাগানো আকর্ষণ জাগাতে চাইছে, তা না বোঝার মতো বোকাও বিভা ছিল না। তাহলে কেন ভালোবেসেও বিভার এই সরে আসা? অভীক একভাবে এই প্রত্যাখ্যানের কারণ ভাবতে চেয়েছে। অভীকের নাস্তিকতা বা নিরীশ্বরবাদ ধর্মবিশ্বাসী বিভাকে তার সঙ্গে মিলতে দিচ্ছে না, এই অনুযোগ সে বিভাকেও জানিয়েছে। কিন্তু এটাও বিভার তরফে আসা প্রত্যাখ্যানের আসল কারণ বলে মনে হয় না। তিনসঙ্গীর শেষকথা গল্পে রুচিরা কেন ডক্টর নবীনমাধব সেনগুপ্তকে ভালোবেসে প্রত্যাখ্যান করেছিল, তার একটা স্পষ্ট কারণ সে জানিয়েছিল। দাম্পত্যের বন্ধন যেন জ্ঞানসাধনার মুক্ত বিশ্বে অর্গল না দেয়। রবিবার গল্পে এরকম স্পষ্ট কোনও কথা বিভার বা গল্পকথকের তরফে বলা হয় নি। কিন্তু অনুমান করা যায় বিভার দ্বিধাজড়িত প্রত্যাখ্যান হয়তো একারণেই। তবে শেষকথা গল্পে রুচিরার প্রত্যাখ্যান যেমন পূর্ণ যতি, রবিবার গল্পে তেমন কিছু নেই। ইউরোপ থেকে যশস্বী হয়ে দেশে ফেরার পর অভীক বিভার সঙ্গে পুনর্মিলিত হবে, এমন সম্ভাবনার দরজা সেখানে খোলা রাখা আছে।
শেষকথা
শেষকথা গল্প তিনসঙ্গীর অন্যান্য দুটি গল্পের চেয়ে কম উচ্চকিত। ল্যাবরেটরি গল্পে অনেক চরিত্রের ভিড়। রবিবার গল্পে সামনে কম জন এলেও অনেকের কথা গল্পে শোনা যায়। শেষকথা গল্পে কিন্তু মূলত তিনটি চরিত্রের মধ্যেই গল্প আনাগোণা করে। রুচিরার অতীত ইতিহাসকে সামনে আনার জন্য কয়েকটি চরিত্রের অবতারণা করতে হয়েছে, কিন্তু মূল গল্পে তাদের কোনও ভূমিকা নেই।
এই গল্পের নায়িকা রুচিরা অতীতে একজনকে মন দিয়েছিল। কিন্তু সরকারী উচ্চপদে চাকরী পাবার পর আরো উঁচু জায়গায় থাকা এক সরকারী আমলার মেয়েকে তিনি বিয়ে করলেন। রুচিরার মন থেকে ব্যক্তি প্রেমিকটি হারিয়ে গেল, তবে প্রথম প্রেমের মধ্যে দিয়ে আসা ভালোবাসার সুবাতাসের স্মৃতিটুকু থেকে গেল। নবীনমাধব সেনগুপ্তের মতো উচ্চশিক্ষিত সফল রুচিবান একজন পুরুষকে পুনরায় মন দেওয়ার ক্ষেত্রে সেই স্মৃতি বাধা হয়ে দাঁড়ায় নি। নবীনমাধব তাঁর মুগ্ধতা খোলাখুলিই জানিয়েছিলেন। তার একমাত্র অভিভাবক, জ্ঞানতাপস আচার্য দাদু এই সম্পর্ককে খুশিমনেই মেনে নিতেন। কিন্তু এসব সত্ত্বেও গল্পের শেষে এল তিনসঙ্গীর গল্পমালার সাধারণ সূত্র – প্রত্যাখ্যান। রবিবার গল্পে প্রত্যাখ্যান কারণটি অস্পষ্ট থাকলেও ল্যাবরেটরি বা শেষ কথাতে তা অস্পষ্ট থাকে নি। রুচিরা যদিও দেখাতে চেয়েছে বৃদ্ধ দাদুর তার সাহচর্য একান্ত প্রয়োজন, তাই দাদুর কাছেই তাকে থাকতে হবে, কিন্তু সেটা যে এই সম্পর্ক তৈরিতে বাধার কারণ নয়, তা সহজেই বোঝা যায়। নবীনমাধব আর রুচিরা দাম্পত্যে বাঁধা পড়লে সেখানে শ্রদ্ধা সম্মানের সবটুকু নিয়েই দাদু থাকতে পারতেন। রুচিরার তরফে আসা প্রত্যাখ্যানের আসল কারণটি অন্য। সে নিজেই সেটা খোলাখুলি জানিয়েছে নবীনমাধবকে। -
“তা হলে কথাটা পরিষ্কার করে বলি। আমার ঐ পঞ্চবটীর মধ্যে ব'সে আপনার অগোচরে কিছুকাল আপনাকে দেখেছি। সমস্ত দিন পরিশ্রম করেছেন, মানেন নি প্রখর রৌদ্রের তাপ। কোনো দরকার হয় নি কারো সঙ্গের। এক-একদিন মনেহয়েছে হতাশ হয়ে গেছেন, যেটা পাবেন নিশ্চিত করেছিলেন সেটা পান নি। কিন্তু তার পরদিন থেকেই আবার অক্লান্ত মনে খোঁড়াখুঁড়ি চলেছে। বলিষ্ঠ দেহকে বাহন ক'রে বলিষ্ঠ মনের যেন জয়যাত্রা চলছে। এমনতরো বিজ্ঞানের তপস্বী আমি আর কখনো দেখি নি। দূরে থেকে ভক্তি করেছি।'
'এখন বুঝি--'
'না, বলি শুনুন। আমার সঙ্গে আপনার পরিচয় যতই এগিয়ে চলল, ততই দুর্বল হল সেই সাধনা। নানা তুচ্ছ উপলক্ষে কাজে বাধা পড়তে লাগল। তখন ভয় হল নিজেকে, এই নারীকে। ছি ছি, কী পরাজয়ের বিষ এনেছি আমার মধ্যে।”
এই চিন্তা যে রুচিরার মধ্যে ঢুকেছিল, সেখানে একদা আলাপকালে নবীনমাধবের কথাবার্তা থেকে উঠে আসা ভাবনার ধরনটি কি কোনওভাবে কোনও ভূমিকা রেখেছিল? প্রাসঙ্গিক অংশটুকু উদ্ধার করা যাক। “প্রসঙ্গক্রমে অচিরা আমাকে বলেছিল, 'আমাদের দেশে মেয়েদের আপনারা পান সংসারের সঙ্গিনীরূপে। সংসারে যাদের দরকার নেই, এ দেশের মেয়েরাও তাদের কাছে অনাবশ্যক। কিন্তু বিলেতে যারা বিজ্ঞানের তপস্বী, তাদের তো উপযুক্ত তপস্বিনী জোটে, যেমন ছিল অধ্যাপক কুরির সহধর্মিণী মাদাম কুরি। সেরকম কোনো মেয়ে আপনি সে দেশে থাকতে পান নি?' মনে পড়ে গেল ক্যাথারিনের কথা। একসঙ্গে কাজ করেছি লণ্ডনে থাকতে। এমন-কি, আমার একটা রিসার্চের বইয়ে আমার নামের সঙ্গে তাঁর নামও জড়িত ছিল। মানতে হল কথাটা। অচিরা বললে, 'তাঁকে আপনি বিয়ে করলেন না কেন। তিনি কি রাজি ছিলেন না।'
আবার মানতে হল, 'হাঁ, প্রস্তাব তাঁর দিক থেকেই উঠেছিল।'
'তবে?'
'আমার কাজ যে ভারতবর্ষের। শুধু সে তো বিজ্ঞানের নয়।'
'অর্থাৎ ভালোবাসার সফলতা আপনার মতো সাধকের কামনার জিনিস নয়। মেয়েদের জীবনের চরম লক্ষ্য ব্যক্তিগত, আপনাদের নৈর্ব্যক্তিক।”
রুচিরা যে জড়াল না তার সঙ্গে সম্পর্কে সেটা কি নবীনমাধবকে একেবারে ভেঙে দিয়েছিল? গল্পের শেষ থেকে এর উত্তর পাওয়া যাবে। “বাড়ি ফিরে গিয়ে কাজের নোট এবং রেকর্ডগুলো আবার খুললুম। মনে হঠাৎ খুব একটা আনন্দ জাগল-- বুঝলুম একেই বলে মুক্তি। সন্ধ্যাবেলায় দিনের কাজ শেষ ক'রে বারান্দায় এসে বোধ হল-- খাঁচা থেকে এসেছে পাখি, কিন্তু পায়ে আছে এক টুকরো শিকল। নড়তে চড়তে সেটা বাজে।” প্রেমের বাষ্প কাজের জগতে স্বচ্ছন্দ বিচরণে যে ছায়া ফেলছিল, তার স্বীকারোক্তি এখানে আছে। সেই ছায়া কেটে যাওয়ার স্বস্তিটাও অস্পষ্ট নয়। তবে এই স্বস্তি যে প্রেমের স্মৃতির যন্ত্রণাকে ঢেকে দিতে পারছে তাও না। শিকলের মতো একটা স্মৃতি পায়ে আটকে থাকছেই।
ল্যাবরেটরি
শেষকথা গল্পে অধ্যাপক কুরী আর মাদাম কুরীর উদাহরণ এসেছি। বিলেতে এমন উদাহরণ নিতান্ত দুর্লভ নয় যেখানে স্বামী স্ত্রী শুধু পরস্পরের জীবন ও যৌনসঙ্গী নয়, কাজ ও চিন্তার সঙ্গীও বটে। এইরকম আমাদের দেশে তখনো সম্ভব নয় বলেই বোধহয় জ্ঞানতাপসদের জ্ঞানচর্চা একখাতে এগোয় আর গৃহিণী সংসারের নিত্যকর্ম নিয়ে দূরে এককোণায় পড়ে থাকেন। এই ব্যবধান কীভাবে ঘোচানো যায় সেটাই ল্যাবরেটরি গল্পের নন্দকিশোরের সারা জীবনের অন্যতম স্বপ্ন ছিল। - “লোকে হাসত যখন দেখত, উনি স্ত্রীকে নিজের বিদ্যের ছাঁচে গড়ে তুলতে উঠেপড়ে লেগে গিয়েছেন। জিজ্ঞাসা করত, 'ও কি প্রোফেসারি করতে যাবে নাকি।' নন্দ বলতেন, 'না, ওকে নন্দকিশোরি করতে হবে, সেটা যে-সে মেয়ের কাজ নয়।' বলত, 'আমি অসবর্ণবিবাহ পছন্দ করি নে।'
'সে কী হে।'
'স্বামী হবে এঞ্জিনীয়র আর স্ত্রী হবে কোটনা-কুটনি, এটা মানবধর্মশাস্ত্রে নিষিদ্ধ। ঘরে ঘরে দেখতে পাই দুই আলাদা আলাদা জাতে গাঁটছড়া বাঁধা, আমি জাত মিলিয়ে নিচ্ছি। পতিব্রতা স্ত্রী চাও যদি, আগে ব্রতের মিল করাও।”
বিদ্বান জ্ঞানতাপস পুরুষ পরিবারের মহিলাদেরও জ্ঞানচর্চার অংশভাগ করে নিতে চাইছেন, এটা তিনসঙ্গীর গল্পগুলির আধুনিকতার অন্যতম অভিজ্ঞান। আমরা শেষকথা গল্পটিতেও দেখেছি জ্ঞানতাপস আচার্য তার স্ত্রী ও নাতনীর সঙ্গে চিন্তাচর্চা ভাগ করে নিতে চাইছেন। বিদ্যাজগতের নানা কিছুতে পরিবারের নারীদের সামিল করতে চাইছেন। এই চেষ্টা ল্যাবরেটরির নন্দকিশোরের মধ্যেও ছিল। পাঞ্জাবে কর্মসূত্রে গিয়ে ‘পতিতা নারী’ সোহিনীর সঙ্গে তিনি পরিচিত হন ঘটনাচক্রে। বুঝতে পারেন এই মেয়েটির মধ্যে আগুনের দীপ্তি আছে। নন্দকিশোর সোহিনীকে বিয়ে করেন ও গড়ে পিঠে নেন। নন্দকিশোরের সমস্ত জীবনের কেন্দ্রে ছিল বিজ্ঞানসাধনা ও সেই সাধনার ভরকেন্দ্র ছিল বহুমূল্যবান নানা যন্ত্রে সাজানো নিজ হাতে তৈরি তার ল্যাবরেটরিটি। এখানে এমন অনেক উপাদান ছিল যা দেশের অনেক বড় বিশ্ববিদ্যালয় বা গবেষণাগারেও ছিল না। এই ল্যাবরেটরিতে কাজ করতে করতেই একদিন দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান নন্দকিশোর। তার মৃত্যুর পর স্ত্রী সোহিনী এক অন্য ও অনন্য অর্থে পাতিব্রত্যের দৃষ্টান্ত স্থাপণ করল। এই পাতিব্রত্য প্রচলিত যৌন শুচিতা ছিল না, বরং প্রকাশ্যেই সেখান থেকে সেখানে সরে এসেছিল। ল্যাবরেটরি রক্ষার জন্য জনৈক অধ্যাপকের থেকে সে অকাতরে সাহায্য পরামর্শ নিচ্ছিল, আর প্রতিদানস্বরূপ তার গলা জড়িয়ে গালে চুমো খেতেও তার আটকায় নি। ল্যাবরেটরি ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য চলাকালীন মামলায় সে উকিলকে যেভাবে বশ করেছিল, তার মধ্যে যৌনতা ছিল তার স্পষ্ট ইঙ্গিৎও গল্পে আছে। পাতিব্রত্যকে যৌন শুচিতা থেকে সম্পূর্ণ বিযুক্ত করে নিয়ে কাজ ও চিন্তার প্রতি বিশ্বস্ততায় স্থাপণ করাটা এক নতুন ও ব্যতিক্রমী দিক এবং এটাই ল্যাবরেটরি গল্পের আধুনিকতা ও বিশিষ্টতার মূল দিক। পাতিব্রত্যের এই নির্দিষ্ট বোধটি যৌন শুচিতাকে যেমন অগ্রাহ্য করতে শিখিয়েছিল সোহিনীকে, তেমনি কন্যাস্নেহ থেকে বেরিয়ে এসে তার প্রতি প্রচণ্ড কঠোর হওয়ার রাস্তাতেও ঠেলে দিয়েছিল। স্বামীর জীবনের সার ল্যাবরেটরির জন্য একজন উপযুক্ত নবীন পরিচালককে সে খুঁজছিল। অধ্যাপকের পরামর্শে রেবতীকে সে কাজের জন্য প্রথমে যোগ্য মনে হয়। এবার মেয়ে নীলাকে তার দিকে এগিয়ে দিয়ে রেবতীকে বশ করতে চায় সোহিনী। কিন্তু যে মুহূর্তে সে দেখে রেবতি প্রেমের আবেগে মাতোয়ারা হয়ে নিজের গবেষণা ও ল্যাবরেটরির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বকে অগ্রাহ্য করছে, সেই মুহূর্তে সে নীলাকে তার থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। এই সময় মা ও মেয়ের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার এক নতুন ধরন আত্মপ্রকাশ করে, যা বাংলা সাহিত্যে নিতান্তই দুর্লভ।
'মা, এত রাগ করছ কেন। ওঁরা নিঃস্বার্থভাবে দেশের উপকার করতে চান।''
'আচ্ছা সে আলোচনা থাক্। এতক্ষণে তুমি বোধ হয় তোমার বন্ধুদের কাছ থেকে খবর পেয়েছ যে তুমি স্বাধীন।'
'হাঁ পেয়েছি।'
'নিঃস্বার্থরা তোমাকে জানিয়েছেন যে তোমার স্বামীর দত্ত অংশে তোমার যে টাকা আছে সে তুমি যেমন খুশি ব্যবহার করতে পারো।'
'হাঁ জেনেছি।'
'আমার কানে এসেছে উইলের প্রোবেট নেবার জন্যে তোমরা প্রস্তুত হচ্ছ। কথাটা বোধ হয় সত্যি?'
'হাঁ সত্যি। বঙ্কুবাবু আমার সোলিসিটর।'
'তিনি তোমাকে আরো কিছু আশা এবং মন্ত্রণা দিয়েছেন।'
নীলা চুপ করে রইল।
'তোমার বঙ্কুবাবুকে আমি সিধে করে দেব যদি আমার সীমানায় তিনি পা বাড়ান। আইনে না পারি বে আইনে। ফেরবার সময় আমি পেশোয়ার হয়ে আসব। আমার ল্যাবরেটরি রইল দিনরাত্রি চারজন শিখ সিপাইয়ের পাহারায়। আর যাবার সময় এই তোমাকে দেখিয়ে যাচ্ছি-- আমি পাঞ্জাবের মেয়ে।'
ব'লে নিজের কোমরবন্ধ থেকে ছুরি বের করে বললে, 'এ ছুরি না চেনে আমার মেয়েকে, না চেনে আমার মেয়ের সোলিসিটরকে। এর স্মৃতি রইল তোমার জিম্মায়। ফিরে এসে যদি হিসেব নেবার সময় হয় তো হিসেব নেব।'
বস্তুত ল্যাবরেটরি গল্প যে সব প্রোটোটাইপ ভেঙেছে মা মেয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী সম্পর্কও তার অন্যতম। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকেই মায়ের নিষেধ ও আক্ষরিক অর্থেই বসান পাহারাকে অতিক্রম করে রেবতীকে যৌবনজ্বালে ফাঁসানোর সর্বাত্মক চেষ্টা করে নীলা। সে যখন প্রায় সিদ্ধকাম হয়েছে, সে সময়েই পাঞ্জাব থেকে ফিরে আসেন সোহিনী ও সমস্ত অস্ত্র প্রয়োগ করে রেবতিকে নীলার থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেন। এ জন্য রেবতীর একমাত্র অভিভাবক, যাকে রেবতী প্রবল ভয় পায়, সেই পিসীমাকেও খুঁজে বের করে কাজে লাগান তিনি। এও বুঝতে পারেন ল্যাবরেটরি রক্ষার কাজে রেবতী কতটা অপদার্থ হবে। শুধু নীলার জীবন থেকেই নয়, ল্যাবরেটরী রক্ষার জায়গা থেকেও তাকে সরিয়ে দেওয়া দরকার।
তিনসঙ্গীর সব গল্পেই নারী পুরুষের খোলামেলা মেলামেশার ছবি আছে, রবিবার গল্পে ভ্রমরবৃত্তির দৃষ্টান্তও অপ্রতুল। কিন্তু ল্যাবরেটরি গল্পে যৌনতা এবং নগ্নতার যে সব প্রকাশ্য ছবি রয়েছে তা রবীন্দ্রসাহিত্যে অদ্বিতীয়।
প্রথম যখন নীলাকে নিয়ে সোহিনী যাচ্ছে রেবতীর কাছে, তখন মেয়েকে সে কীভাবে সাজিয়েছে তা দেখা যাক। “মেয়েকে নিয়ে মোটরলঞ্চে করে উপস্থিত হল বোটানিকালে। তাকে পরিয়েছে নীলচে সবুজ বেনারসী শাড়ি, ভিতর থেকে দেখা যায় বাসন্তী রঙের কাঁচুলি। কপালে তার কুঙ্কুমের ফোঁটা, সূক্ষ্ণ একটু কাজলের রেখা চোখে, কাঁধের কাছে ঝুলেপড়া গুচ্ছকরা খোঁপা, পায়ে কালো চামড়ার 'পরে লাল মখমলের কাজ-করা স্যাণ্ডেল।” এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য - ভিতর থেকে দেখা যায় বসন্তী রঙের কাঁচুলি – এই অংশটি। মেয়ে নীলার বুকের আদলকে মা সোহিনী রেবতির কাছে প্রকাশ্য করে তুলতে চাইছে, এ নিঃসন্দেহে এক নজরকাড়া উপস্থাপণ।
নীলার শরীরী বিভঙ্গের ছবি কীভাবে এই গল্পে এসেছে, উদাহরণস্বরূপ সেই অংশটি আমরা খেয়াল করতে পারি।
“নীচের ঘড়িতে দুটো বাজল। মুহূর্তের জন্য রেবতী তার চিন্তার বিষয় ভাবছিল জানলার বাইরে আকাশের দিকে চোখ মেলে।
এমন সময়ে দেওয়ালে পড়ল ছায়া। চেয়ে দেখে ঘরের মধ্যে এসেছে নীলা। রাত-কাপড় পরা, পাতলা সিল্কের শেমিজ। ও চমকে চৌকি থেকে উঠে পড়তে যাচ্ছিল। নীলা এসে ওর কোলের উপর বসে গলা জড়িয়ে ধরল। রেবতীর সমস্ত শরীর থর্ থর্ করে কাঁপতে লাগল, বুক উঠতে পড়তে লাগল প্রবলবেগে। গদ্গদ কণ্ঠে বলতে লাগল, 'তুমি যাও, এ ঘর থেকে তুমি যাও।'
ও বললে, 'কেন।'
রেবতী বললে, 'আমি সহ্য করতে পারছি নে। কেন এলে তুমি এ ঘরে।'
নীলা ওকে আরো দৃঢ়বলে চেপে ধরে বললে, 'কেন, আমাকে কি তুমি ভালোবাস না।'
রেবতী বললে, 'বাসি, বাসি, বাসি। কিন্তু এ ঘর থেকে তুমি যাও।'…
রাত-কাপড়ের ভিতর থেকে নীলার নিখুঁত দেহের গঠন ভাস্করের মূর্তির মতো অপরূপ হয়ে ফুটে উঠল, রেবতী মুগ্ধ চোখে না দেখে থাকতে পারল না। নীলা চলে গেল। রেবতী টেবিলের উপর মুখ রেখে পড়ে রইল। এমন আশ্চর্য সে কল্পনা করতে পারে না। একটা কোন্ বৈদ্যুত বর্ষণ প্রবেশ করেছে ওর শিরার মধ্যে, চকিত হয়ে বেড়াচ্ছে অগ্নিধারায়।”
এই বর্ণনায় – ‘রাত-কাপড় পরা, পাতলা সিল্কের শেমিজ’ আর সেই ‘রাত-কাপড়ের ভিতর থেকে নীলার নিখুঁত দেহের গঠন ভাস্করের মূর্তির মতো অপরূপ হয়ে ফুটে’ ওঠার বর্ণনা লিখছেন জীবন সায়াহ্নে পৌঁছনো ঊন-আশি বছরের রবীন্দ্রনাথ, একথা ভেবে খানিক আশ্চর্য লাগে বৈকি। বোঝা যায় শিল্পের প্রয়োজনে গুরুদেব মূর্তি ভেঙে নতুন রূপে আত্মপ্রকাশে তাঁর কোনও দ্বিধা ছিল না।
হিতবাদী পত্রিকায় লেখা রবীন্দ্র গল্পের আলোচনার লিংক
সাধনা পত্রিকায় লেখা রবীন্দ্র গল্পের আলোচনার লিংক